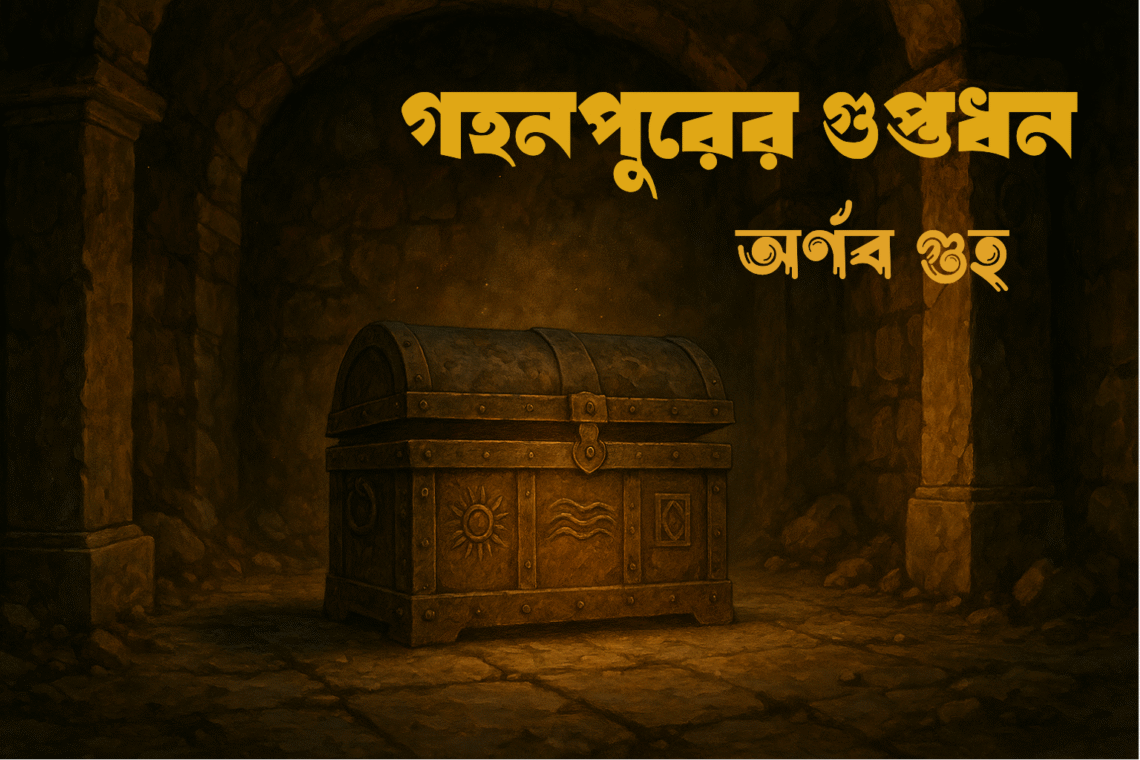অর্ণব গুহ
অধ্যায় ১: হারিয়ে যাওয়া নোটবই
গহনপুর – নামটায় এক রকম রহস্য আছে। বাঁকুড়া জেলার শেষ প্রান্তে অবস্থিত এই ছোট্ট গ্রামটার ইতিহাস কতদূর ছড়িয়ে, কেউ তা স্পষ্ট বলতে পারে না। জঙ্গলে ঘেরা, পিচঢালা রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই এই গহনপুর। গ্রামের মধ্যে এখনও কিছু টালির ছাউনি ঘর, একটা ভাঙা জমিদার বাড়ি আর একটা প্রাচীন শিবমন্দির—কোনটা কবে তৈরি, সঠিক কেউ জানে না।
সেই গহনপুরেই পৌঁছল তিনজন বন্ধু—সুদীপ্ত, ঐন্দ্রিলা আর বাপি। কলকাতার স্কুলজীবনের বন্ধুত্ব এখন কাজের চাপে একটু আলগা হলেও, এই রহস্যময় আমন্ত্রণ তাদের আবার এক করল।
“এই বাড়িটা তো একেবারে হন্টেড সিনেমার মতো!”—বাপি গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলে।
ঐন্দ্রিলা একটু হেসে বলে, “চুপ কর, বাপি। গম্ভীর ব্যাপারে এসেছি আমরা।”
সুদীপ্ত, যার ঠাকুরদা সুবীর মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, সে-ই এই গোটা অভিযানটার কেন্দ্রবিন্দু। সুদীপ্তর ঠাকুরদা বহু বছর আগে গহনপুরে এসে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের কেউ কখনও সঠিকভাবে জানতে পারেনি উনি কোথায় গেলেন, কী খুঁজছিলেন। কিছু চিঠিপত্র আর পুরনো বই ছাড়া কিছুই রেখে যাননি তিনি।
কিন্তু মাসখানেক আগে, হঠাৎই এক চিঠি এসে পৌঁছয় সুদীপ্তর কাছে—একটা অচেনা হাতে লেখা, যেন ধুলো ধরা পুরনো কাগজ। তাতে লেখা:
“যদি সত্যিই তুমি সুবীরবাবুর নাতি হও, তবে গহনপুরে এসো। তিনি যেটা খুঁজছিলেন, সেটা এখনও রয়ে গেছে। একটা পুরনো নোটবই তোমার উত্তর লুকিয়ে রেখেছে।”
চিঠির নিচে কোনো নাম নেই, শুধু একটা ম্যাপের মতো আঁকা—একটা ছোট খালের পাশ দিয়ে একটা বাড়ির চিহ্ন, আর একটা শিবমন্দির।
আজ সেই ম্যাপ অনুসরণ করেই তারা পৌঁছেছে।
গহনপুরের একমাত্র চায়ের দোকানে থেমে ওরা একটু খবর নিতে চায়। দোকানদার, বছর ষাটের এক লোক, নাম তার পাণ্ডু কাকা, চোখে ময়লা চশমা। সে বলল, “সুবীরবাবু? আরে হ্যাঁ, অনেক বছর আগে এসেছিলেন। জমিদার বাড়িটার দোতলায় থাকতেন ক’দিন। তারপর হঠাৎই উধাও! আপনারা ওঁর আত্মীয়?”
সুদীপ্ত মাথা নাড়ে। “উনি কী খুঁজছিলেন, জানেন?”
পাণ্ডু কাকা মাথা চুলকে বলে, “তেমন কিছু না… তবে লোকেরা বলে উনি গুপ্তধনের খোঁজ করছিলেন। জমিদারদের শেষ কালের কিছু নথি নিয়ে খুব আগ্রহ ছিল।”
সেই জমিদার বাড়িটাই এখন ওদের গন্তব্য।
বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে প্রকৃতির মুখোমুখি, ধ্বংসস্তূপের মতো। লতাপাতা ঢেকে ফেলেছে জানলা, দরজার কপাট অর্ধেক খোলা। তবে ঘরে ঢুকতেই এক অদ্ভুত গন্ধ—ধুলো, পুরোনো কাগজ আর সময়ের।
ঐন্দ্রিলা মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে দেয়। দোতলায় একটা ঘর, যেখানে একটা পুরনো কাঠের টেবিল আর ভাঙা বুকশেলফ দেখা যায়। হঠাৎ বাপির চোখে পড়ে, মেঝের একটা ঢাকনা আলগা।
“এটা খুলে দেখবি?”—সে বলে।
ওরা ঢাকনাটা খুলতেই একটা কাঠের বাক্স—ভেতরে একটা নোটবই, ধুলো জমা পাতাগুলো নাড়তে গিয়ে সুদীপ্তর হাত কেঁপে ওঠে। নোটবইটা ঠাকুরদারই লেখা! নাম লেখা আছে: “গহনপুর অভিযান – সুবীর মুখোপাধ্যায়”।
প্রথম পাতায় লেখা:
“যদি কেউ একদিন এটা পড়ে, তবে জেনে রেখো, আমি যা খুঁজছি, তা শুধু ধন-সম্পদ নয়। এটা ইতিহাস, এটা উত্তরাধিকার। গহনপুরের শেষ জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর মৃত্যুর আগে একটি ‘তাম্রচৌকি’ লুকিয়ে রেখে গেছেন, যার ভিতর একটি সংকেত লুকানো আছে—যেটা নিয়ে যাবে তোমাকে আসল গুপ্তধনের ঠিকানায়।”
বইয়ের শেষ পাতায় একটা মানচিত্র আঁকা—তবে এটা আগের ম্যাপের চেয়ে জটিল। খাল, মন্দির, শ্মশান, আর একটা অজানা নাম লেখা আছে—“কালসত্র”।
বাপি বলে, “কালসত্র? এটা আবার কোথায়?”
পাণ্ডু কাকার কথায় ফিরে এসে জানা গেল, কালসত্র হল গহনপুরের একটা পুরনো পোড়োবাড়ির নাম, যেটা এখন জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে।
ঐন্দ্রিলা বলে, “এই নোটবইটাই তো আমাদের প্রথম চাবি। মনে হচ্ছে, এবার একটা সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চার শুরু হতে চলেছে।”
সুদীপ্ত চোখ বন্ধ করে ঠাকুরদার ছবিটা মনে করে। মনে মনে বলল,
আমি এসেছি দাদু, এবার আমি তোমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করব।
অধ্যায় ২: কালসত্রের সংকেত
সকালটা ছিল কুয়াশায় মোড়া। গহনপুরের জঙ্গলের ভেতর আলো ঢুকতে যেন লজ্জা পাচ্ছিল। সেই আলোয় তিনজনের মুখে ছায়া আর উত্তেজনা পাশাপাশি খেলা করছিল।
সুদীপ্তর হাতে ঠাকুরদার নোটবই, পেছনের পাতার মানচিত্রে আঙুল রেখে সে বলে উঠল, “দেখো, এই দিকটা হচ্ছে খালের পাশ। আর এটাই কালসত্র।”
বাপি চোখ গোল করে বলল, “মানে এই জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হবে আমাদের?”
ঐন্দ্রিলা একটু হাঁপিয়ে বলল, “এত সহজ হলে তো দাদুর খোঁজের প্রয়োজনই হতো না।”
পাণ্ডু কাকা একটা লাঠি হাতে এসে দাঁড়ায় সামনে। “কালসত্র ওই দিকেই… তবে সাবধানে যেও। জায়গাটা এখন প্রায় জনমানবহীন। শোনা যায় সেখানে রাতে কিছু শোনা যায়—চেনা আর অচেনার মাঝামাঝি শব্দ।”
সুদীপ্ত কাকাকে কৃতজ্ঞতায় মাথা নাড়ে।
তিনজন হাঁটা শুরু করে।
জঙ্গলটা যেন একটা জীবন্ত কাহিনি—সবুজের গায়ে চাপা ইতিহাস, ছেঁড়া পাতার নিচে চাপা শব্দ, গাছের গায়ে খোদাই করা নাম। ঘন্টাখানেক হাঁটার পর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে তারা। মাথার ওপর ছাউনির মতো গাছ, আর ঠিক সামনে একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত পোড়োবাড়ি। একটা বড় গেট, গেটে ধাতব পিতলের পাতে লেখা—”কালসত্র”।
সুদীপ্ত নিচু স্বরে বলল, “ঠিক নাম। এটা-ই কালসত্র।”
তারা গেট ঠেলে ভেতরে ঢোকে। ভিতরে একটা সরু রাস্তা, দুই ধারে ধ্বস্ত দেয়াল, আর মাঝখানে একটা ঘর। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই চোখে পড়ে — একটা পাথরের পিঁড়ি আর তার ওপরে একটা ঢেকে রাখা কিছু। কাপড় সরাতেই বেরিয়ে আসে তাম্রচৌকি!
“দাদু ঠিকই বলেছিলেন!” — ঐন্দ্রিলা অবাক হয়ে বলে ওঠে।
তাম্রচৌকিতে খোদাই করা কিছু চিহ্ন — একটা সূর্য, একটা নদীর রেখা, এবং তিনটে বর্ণ — “ব-চ-ত”। নিচে লেখা:
“যে জানে জলের শব্দ, সেই পৌঁছাবে আলোয়।”
“এই ‘ব-চ-ত’ কী হতে পারে?” — বাপি বলল।
সুদীপ্ত বলল, “এটা যদি সংকেত হয়, তাহলে সম্ভবত কোনো নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। হয়তো নদীর নাম, বা কোনো গ্রামের?”
তখনই ঐন্দ্রিলা বলে ওঠে, “দেখো, নোটবইয়ের এক জায়গায় লেখা আছে — ‘দক্ষিণ দিকে গিয়ে নদীর ধারে যে মন্দির, তার পাশেই গোপন চিহ্ন আছে।’”
সুদীপ্ত মাথা নাড়ে। “তবে আমাদের এবার যেতে হবে নদীর দিকে। গহনপুরের দক্ষিণে একটা নদী আছে—চিত্রানদী। ওখানেই হয়তো পরবর্তী সূত্র।”
তারা আবার যাত্রা শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের গন্ধ বদলে যায়, কাঁকড়ানো মাটি থেকে পাথুরে ঢালু, তারপর একসময় নদীর ধারে পৌঁছে যায় তারা। নদীর গর্জন নেই, তবে স্রোত চলমান, যেন অতীতের স্মৃতি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
নদীর ধারে একটা ছোট মন্দির, প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। কিন্তু গায়ে গায়ে অদ্ভুত চিহ্ন—গোলাকার সূর্য, তার নিচে একটা খুদে মানচিত্র খোদাই করা।
বাপি বলে, “এটা দেখে মনে হচ্ছে পরবর্তী পথের মানচিত্র!”
ঐন্দ্রিলা তখন খুব শান্ত গলায় বলে, “এই তো অ্যাডভেঞ্চার! ভাবতেই পারিনি আমরা সত্যিই ঠাকুরদার পথ ধরে এগোতে পারব।”
সুদীপ্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তার চোখে জল। সে যেন নিজের ঠাকুরদার ছায়ার কাছে পৌঁছে গেছে।
হঠাৎই পেছনে একটা শব্দ হয়।
ঝোপের ভেতর কেউ যেন নড়ল।
তারা তিনজন ঘুরে দাঁড়ায়।
একজন বয়স্ক লোক, গায়ে ধুতি, হাতে বাঁশের লাঠি, চুল পাকা। সে শান্ত গলায় বলল,
“তোমরা সুবীরবাবুর পথ ধরে এসেছো, বুঝি?”
সুদীপ্ত অবাক হয়ে বলে, “আপনি কে?”
লোকটা একটু হাসে। “আমার নাম—ধৃতিমান। আমি ছিলাম তোমার ঠাকুরদার সহকারী। উনি যখন এই পথ অনুসন্ধান করছিলেন, তখন আমি ছিলাম তার চোখ-কান।”
তিনজন একসঙ্গে চুপ।
ধৃতিমান বলল, “তোমাদের হাতে যা আছে, তার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করছে। কিন্তু সাবধান, এই খোঁজ যেমন ইতিহাস রক্ষা করতে পারে, তেমনি নষ্টও করতে পারে।”
বলে সে এগিয়ে এসে তাম্রচৌকির একটা দাগে আঙুল রাখে।
“এই চিহ্ন মানে শুধুই পথ নয়, এর মানে আছে—একটা পাপ, একটা অভিশাপ। তবে সেটা বুঝবে শেষ চিহ্নে পৌঁছালে।”
তাদের সামনে এবার খুলে গেল আরেকটা রহস্যের দরজা।
অধ্যায় ৩: অভিশপ্ত মানচিত্র
ধৃতিমানর মুখে ‘অভিশাপ’ শব্দটা শুনে একটা অজানা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল তিন বন্ধুর মেরুদণ্ডে। গহনপুরের শান্ত দুপুরটা যেন হঠাৎই ভারী হয়ে উঠল।
“আপনি কী বললেন? অভিশাপ?” — বাপি প্রথমে প্রশ্ন করল।
ধৃতিমান মাথা নাড়লেন, “হ্যাঁ। শেষ জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ গুপ্তধনের চিহ্ন রেখে গিয়েছিলেন শুধু উত্তরাধিকারীদের জন্য। কিন্তু যখন তাঁকে ব্রিটিশদের কাছ থেকে গোপন কিছু জিনিস লুকিয়ে রাখতে হয়, তখন তিনি এক প্রাচীন শপথ নিয়েছিলেন—যদি অযোগ্য কেউ এটা খুঁজে পায়, তাহলে ধ্বংস হবে শুধু গুপ্তধন নয়, তার সাথের ইতিহাসও।”
ঐন্দ্রিলা ধীরে ধীরে বলল, “তাহলে আপনি ঠাকুরদার সঙ্গেই ছিলেন, তাই তো?”
ধৃতিমান চোখ বন্ধ করে বললেন, “সুবীরবাবু ছিলেন সত্যিকারের গবেষক। উনি শুধু ধন খুঁজছিলেন না—উনি খুঁজছিলেন সত্য। কিন্তু এক রাতে উনি হঠাৎ হারিয়ে যান। শুধু একটা জিনিস রেখে গিয়েছিলেন আমার কাছে।”
সে নিজের কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল—পুরোনো, প্রায় ছেঁড়া একখানা মানচিত্র। নীল কালিতে আঁকা নদী, গাছপালা, ঘরবাড়ি, আর একটা বড়ো লাল গোলচিহ্ন—সেখানে লেখা “চূড়ান্ত সংকেত”।
সুদীপ্ত কাগজটা নিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলল, “এটা তো সেই মানচিত্রেরই পরবর্তী অংশ!”
মানচিত্র অনুসারে জায়গাটার নাম—শালডাঙ্গা গুহা। ধৃতিমান বললেন, “এই গুহা শুধু স্থান নয়, এটা এক ইতিহাসের পেটিকা। ভিতরে থাকবে শেষ সংকেত, কিন্তু ওখানে যেতে হলে তোমাদের প্রমাণ করতে হবে—তোমরা যোগ্য।”
বাপি একটু খেঁকিয়ে বলল, “মানে? আমরা কীভাবে প্রমাণ করব?”
ধৃতিমান চোখ বন্ধ করে বলল, “একটা ধাঁধা আছে সেখানে। সেটা যদি ঠিকঠাক না বলতে পারো, তাহলে দরজা খুলবে না। খারাপ কিছুও ঘটতে পারে।”
ঐন্দ্রিলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে বলল, “আমরা যাব। যত বিপদই থাকুক না কেন, আমাদের এই খোঁজ শেষ করতে হবে। এটা শুধু গুপ্তধনের জন্য নয়, সুবীর মুখোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত কাজের জন্য।”
তারা পরদিন সকালে রওনা দেয় শালডাঙ্গা গুহার দিকে। পথটা সহজ ছিল না। কাঁটাঝোপ, পাহাড়ি চূড়া, সরু পাথুরে রাস্তা পেরিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা হেঁটে গিয়ে তারা পৌঁছল এক পাহাড়ের গা ঘেঁষা গুহার মুখে।
গুহার প্রবেশপথ একেবারে ঢাকা ছিল ঝোপে। ওদের টর্চে দেখা গেল গুহার দেওয়ালে খোদাই করা চিহ্ন—তাম্রচৌকির মতোই সূর্য, নদী, আর নিচে এক লাইন ধাঁধা:
“যে আলো দেখে না, অথচ পথ দেখায়—তাকে চিনলে খুলবে দ্বার।”
তিনজন থমকে যায়। বাপি বলে, “আলো দেখে না, অথচ পথ দেখায়? এ আবার কেমন ধাঁধা?”
ঐন্দ্রিলা বলে, “চিন্তা করে দেখো—এটা কোনো কিছুর রূপক। এমন কিছু যা নিজে দেখতে পায় না, কিন্তু অন্যকে পথ দেখায়।”
সুদীপ্ত হঠাৎ বলে ওঠে, “তারা!”
ঐন্দ্রিলা ঘুরে তাকায়, “তারা?”
“হ্যাঁ! তারা তো নিজের আলোয় জ্বলে না, সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে। তবু পথ দেখায়, নাবিকদের দিক নির্দেশ করে। তারাই তো সত্যিকারের পথপ্রদর্শক।”
ধৃতিমান হেসে মাথা নাড়েন। “ঠিক উত্তর।”
সঙ্গে সঙ্গে গুহার পাথরের দরজা এক নিমেষে সরে যায়। ভিতরে নেমে যায় সরু সিঁড়ি—অন্ধকার, শীতল, আর একটা অজানা উত্তেজনায় ভরা।
তারা সিঁড়ি ধরে নামতে থাকে।
ভেতরে একটা বিশাল খোলা কক্ষ—চারপাশে পাথরের স্তম্ভ, মাঝখানে রাখা একটি ধাতব সিন্দুক। সেই সিন্দুকে খোদাই করা—”গহনপুরের শেষ ইতিহাস”।
তাদের সামনে এখন খুলে গেল চূড়ান্ত চাবি।
কিন্তু হঠাৎই বাইরে বাজ পড়ল, আর এক মুহূর্তে গুহার ভিতর বাতাস কেঁপে উঠল।
“তোমরা প্রস্তুত তো?” — ধৃতিমান জিজ্ঞেস করলেন।
সুদীপ্তর উত্তর স্পষ্ট: “এখন আর পেছনে ফেরার উপায় নেই।”
অধ্যায় ৪: ইতিহাসের সিন্দুক
গুহার ভেতরটা যেন কোনো যুগের ফসিল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া নিঃশব্দতা এখানে জমাট বেঁধে আছে। সিন্দুকটার চারদিকে তিনজন দাঁড়িয়ে, মাঝখানে ধৃতিমান।
সিন্দুকটা খুব বড়ো নয়, কিন্তু তার ভার অনুভব করা যায়—এটা যেন শুধু ধাতব বস্তু নয়, এক জাতীয় নৈতিক দায়িত্ব।
সুদীপ্ত ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে সিন্দুকের ঢাকনা স্পর্শ করল। ততক্ষণে বাইরে ঝড় শুরু হয়েছে। বাতাসের শব্দ ভিতরের নীরবতাকে ভেঙে দিচ্ছে।
ধৃতিমান বললেন, “এটা খোলার আগে একটা কথা মনে রাখো—এই সিন্দুকের ভিতরে শুধু ধন নয়, এমন কিছু আছে যা ইতিহাসকে বদলে দিতে পারে। তোমার ঠাকুরদা সেটাকেই খুঁজছিলেন, কারণ সেটা হারালে একটা প্রজন্ম তার শিকড় হারিয়ে ফেলত।”
ঐন্দ্রিলা ধীর গলায় বলল, “তাহলে শুরু করি।”
সুদীপ্ত সিন্দুকের ওপরে থাকা তিনটা খুদে চাবির গর্তে ঠাকুরদার নোটবই থেকে পাওয়া তাম্রচাবিটা ঢোকায়। একটু কষ্ট হলেও ঘুরে যায়। সিন্দুক খুলে যায় ধীরে ধীরে।
ভেতরে ছিল—
১. একটি পুরনো পাণ্ডুলিপি, শালপাতায় লেখা।
২. একটি ছোট চৌকো কাঠের বাক্স, যার গায়ে অদ্ভুত প্রতীক।
৩. আর ছিল একটি চিঠি, সুবীর মুখোপাধ্যায়ের নিজের হাতে লেখা।
প্রথমে তারা চিঠিটা খুলে পড়ে।
“এই সিন্দুক খুলে যে পৌঁছেছে, জেনে রেখো—তুমি ইতিহাসের শেষ সত্য জানার জন্য প্রস্তুত। গহনপুরের জমিদার বংশ কোনো সাধারণ জমিদার পরিবার ছিল না। তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়ক ছিল, ব্রিটিশদের চোখে ‘বিপজ্জনক’। সেই সময়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে গোপন বিপ্লবী দল গহনপুরে আশ্রয় নিত। এই পাণ্ডুলিপি সেই সময়েরই দলিল। এটা হারালে শুধু একটা অঞ্চল নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অলিখিত অধ্যায় হারিয়ে যাবে।”
চিঠির শেষে লেখা—
“তুমি যদি সত্যিই উত্তরসূরি হও, তবে এই ইতিহাসকে আলোয় আনো। সেটা হলেই আমি শান্তি পাবো।”
সুদীপ্তর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ঠাকুরদার হাতের লেখা যেন তাকে স্পর্শ করছে। বাপি আর ঐন্দ্রিলা চুপ। কেউ কোনো শব্দ করছিল না।
পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো আলতো করে খোলা হয়।
তাতে ছিল হাতে লেখা লিপি—বাংলা ও সংস্কৃতের এক মিশ্র রূপে। বিপ্লবীদের নাম, তারিখ, গহনপুরের এক গোপন সুড়ঙ্গের মানচিত্র, এমনকি সেই সময়কার অস্ত্র মজুদের বর্ণনা।
ঐন্দ্রিলা বিস্মিত হয়ে বলে, “এই তো ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া টুকরো!”
সুদীপ্ত বলল, “আমাদের এটা সংরক্ষণ করতে হবে। এগুলো জাদুঘরে গেলে মানুষ জানবে, কীভাবে একটা ছোট গ্রাম স্বাধীনতার আঁচল হয়ে উঠেছিল।”
বাপি হেসে বলে, “তাহলে তো গুপ্তধনের চাইতেও বড় কিছু পেয়ে গেছি আমরা।”
তখনই ধৃতিমান সেই ছোট কাঠের বাক্সটা খোলেন।
ভেতরে ছিল কিছু পুরনো রৌপ্য মুদ্রা, এক জোড়া শঙ্খের চুড়ি, আর একটা সোনার পিন—সম্ভবত জমিদার বংশের কোনো গোপন সঞ্চয়। ধৃতিমান বললেন, “এইটুকুই বাঁচানো গিয়েছিল। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো জিনিস হলো পাণ্ডুলিপি। এর মূল্য টাকায় হয় না—এটা জাতির স্মৃতি।”
তখন হঠাৎই ঐন্দ্রিলা বলল, “আমরা এসব নিয়ে বাইরে গেলে, কেউ যদি এগুলো ছিনিয়ে নিতে চায়?”
ধৃতিমান চুপ করে বললেন, “এই গুহার পেছনে সুড়ঙ্গ আছে। তোমার ঠাকুরদা সেটা চিনতেন। আমি সেটাই ব্যবহার করেছিলাম ওঁর লেখা জিনিসপত্র সংরক্ষণ করতে।”
সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, “তাহলে আমরা সেই পথ ধরেই ফিরব?”
ধৃতিমান বললেন, “হ্যাঁ। তবে আগে এই জিনিসগুলো একটা ব্যাগে গুছিয়ে ফেলো। আজ থেকে তোমাদের দায়িত্ব শুরু।”
গুহার দেওয়ালে রাখা লুকোনো সুইচে চাপ দিতেই একটা পাথরের দরজা খুলে যায়—তার পেছনে অন্ধকার সুড়ঙ্গ। তারা সেই পথেই যাত্রা শুরু করে।
পিছনে রয়ে যায় সিন্দুক। আর তার পাশে একটি লাল কাপড়ে মোড়া পাথর, যাতে খোদাই করা—
“যারা ইতিহাসকে মরতে দেয় না, তারা চিরকাল বেঁচে থাকে।”
অধ্যায় ৫: ফিরে দেখা অতীত
সুড়ঙ্গটা সরু, স্যাঁতসেঁতে আর প্রায় নিঃশব্দ। মাঝে মাঝে বাদুড়ের আওয়াজ, কখনো ঠান্ডা বাতাসে কেঁপে ওঠা জোনাকি আলোর মতো অনুভূতি। তিন বন্ধু ধৃতিমানকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেকের কাঁধে এখন শুধু একটা ব্যাগ নয়, এক বিশাল ইতিহাসের ভার।
বাপি ধীরে ধীরে বলে উঠল, “ভাবিনি আমাদের ছুটি কাটাতে এসে এরকম এক অভিযানে জড়িয়ে পড়ব।”
ঐন্দ্রিলা হেসে বলল, “এটা তো ছুটি নয়, এটা তো নিজের শিকড় খোঁজার চেষ্টা।”
সুদীপ্ত চুপ করে হাঁটছিল। হঠাৎ একটা জায়গায় এসে ধৃতিমান থেমে গেলেন। গুহার দেয়ালে ঝোলানো এক পিতলের টুকরোতে সূর্য, নদী, আর ‘স’ অক্ষর খোদাই করা।
তিনি বললেন, “তোমাদের ঠাকুরদা এই জায়গা অবধিই এসেছিলেন। কিন্তু এর পরেই উনি নিখোঁজ হন। কেউ কেউ বলে, তিনি কোনো চিঠি পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পৌঁছায়নি।”
সুদীপ্ত ব্যাগ থেকে সেই অচেনা চিঠিটা বের করে দেখায়—“এইটা?”
ধৃতিমান কাগজটা দেখে চমকে উঠলেন। “এটা তো আমি লিখেছিলাম! ঠিক এই গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে পোস্ট করেছিলাম তোমার নাম করে। অনেক দিন পর খুঁজে পেয়েছিলাম, তোমার দাদু হয়তো কোথাও একটা চিহ্ন রেখেছিলেন তোমার জন্য।”
একটু থেমে ধৃতিমান বললেন, “তোমার ঠাকুরদার শেষ কিছু লিপি আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম একটা পুরনো কুয়োর ভেতরে। সেটাই ছিল তার অসমাপ্ত গবেষণার কেন্দ্র। এখন যদি চাও, সেটা আমি তোমাদের দেখাতে পারি।”
তিন বন্ধু একসাথে মাথা নাড়ল।
সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে তারা পৌঁছাল গহনপুরের মন্দির চত্বরে। মন্দিরটা ভেঙে পড়লেও পাশের কুয়োটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে—ঢাকনা লাগানো, উপরে কিছু পাথর রাখা।
ধৃতিমান পাথর সরিয়ে ঢাকনা খুলে একটা লোহার দড়ি নামালেন। কিছুক্ষণ পর তিনি একটা টিনের বাক্স তুলে আনলেন।
ভেতরে যা ছিল, তা এক কথায় অমূল্য।
১. গহনপুর রাজবংশের বংশলতিকা
২. ব্রিটিশ বিরোধী সভার হাতে লেখা রেজিস্টার
৩. ঠাকুরদার হাতে লেখা ডায়েরি—তাঁর চিন্তাভাবনা, সংশয়, আশা-নিরাশার কথা
ডায়েরির এক পৃষ্ঠায় লেখা ছিল:
“আমি জানি, আমি হয়তো শেষ করতে পারব না। কিন্তু চাই কেউ একজন হোক, যে আমার কাজটা সম্পূর্ণ করবে। গহনপুর শুধু একটা জায়গা নয়, এটা একটা অধ্যায়—যেটা হারিয়ে যেতে দিতে পারি না।”
সুদীপ্ত চোখের জল সামলাতে পারে না। ঐন্দ্রিলা তাকে কাঁধে হাত রাখে। বাপিও চুপচাপ দাঁড়িয়ে।
সন্ধ্যা নামছে। গহনপুরের আকাশে তখন আভা। বাতাসে শালগাছের পাতার শব্দ।
ধৃতিমান বললেন, “তোমরা এখন কী করবে?”
সুদীপ্ত বলল, “এই ইতিহাস আমরা কলকাতায় নিয়ে যাব। সংরক্ষণ করব। জাদুঘর বা গবেষণা কেন্দ্রে জমা দেব। আর তোমার নামও থাকবে দাদুর পাশে।”
ধৃতিমান হেসে বললেন, “তাহলেই শান্তি পাব। এতদিন যে বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছিলাম, আজ সেটা মুক্তি পেল।”
মন্দির চত্বর তখন শান্ত, কিন্তু বাতাসে যেন কেউ
ফিসফিস করে বলছে—“ধন্য তুমি, ইতিহাসের রক্ষক।”
অধ্যায় ৬: উত্তরাধিকার
কলকাতায় ফিরে আসার পর দিনগুলো যেন ঘনিয়ে আসে। বই, দলিল, পাণ্ডুলিপি—সব কিছু একটা নতুন আলোয় দেখা শুরু করে সুদীপ্ত, ঐন্দ্রিলা আর বাপি।
গহনপুরের সেই অভিযান ছিল শুধু এক অভিযান নয়—একটা ব্যক্তিগত জার্নি, এক উত্তরাধিকার বুঝে নেওয়ার এবং তাকে বহন করার দায়িত্ব।
তারা প্রথমেই যোগাযোগ করল ইন্ডিয়ান হেরিটেজ অ্যান্ড হিস্ট্রি আর্কাইভস-এর সঙ্গে। অধ্যাপক বিভাস রায়, যিনি সেই সংস্থার ইতিহাস গবেষণা শাখার প্রধান, প্রথমেই বলে ওঠেন—
“সুবীর মুখোপাধ্যায়ের নাম আমরা জানি। উনি শেষদিকে নিখোঁজ হন বলেই তো এই অধ্যায় অসম্পূর্ণ ছিল। আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে আপনি উত্তরসূরি, তাহলে এটা ঐতিহাসিক আবিষ্কার হিসেবে স্বীকৃত হবে।”
সুদীপ্ত শুধু মাথা নাড়ে না, সে তুলে ধরে—
ঠাকুরদার নোটবই
গহনপুর রাজবংশের পাণ্ডুলিপি
ব্রিটিশ বিরোধী সভার গোপন দলিল
সেই সোনার পিন ও রৌপ্য মুদ্রা
এবং… ঠাকুরদার শেষ লেখা ডায়েরি
বিভাস রায় চোখে চশমা পরে সব দেখে বলেন, “অবিশ্বাস্য। এই জিনিসগুলো শুধু সংগ্রহ নয়, এগুলো ইতিহাস বদলে দিতে পারে।”
তিনমাসের মধ্যে “গহনপুরঃ ইতিহাসের একটি হারিয়ে যাওয়া অধ্যায়” নামে একটি বিশেষ প্রদর্শনী শুরু হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। ডায়েরির পৃষ্ঠায় লেখা থাকে:
“এই সংগ্রহশালা সুবীর মুখোপাধ্যায় ও তার উত্তরসূরি সুদীপ্তর নামে উৎসর্গীকৃত।”
প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিন ভিড় উপচে পড়ে। সাংবাদিক, ইতিহাসবিদ, গবেষক, ছাত্রছাত্রী সবাই দেখছে সেই সিন্দুক, সেই পাণ্ডুলিপি, সেই নোটবই।
আর সুদীপ্ত, ঐন্দ্রিলা, বাপি দাঁড়িয়ে থাকে পেছনের সারিতে—চুপচাপ, গর্বিত, কিন্তু বিনয়ী।
এক সাংবাদিক এসে জিজ্ঞেস করে, “আপনারা যখন শুরু করেছিলেন, তখন কি জানতেন কোথায় পৌঁছাবেন?”
বাপি হেসে বলে, “না। আমরা শুধু জানতাম, একজন মানুষ অসমাপ্ত কিছু রেখে গেছেন। সেটা পূর্ণ করাটাই ছিল আমাদের লক্ষ্য।”
ঐন্দ্রিলা বলে, “এটা আমাদের তিনজনের জন্যই একটা রূপান্তর ছিল। গহনপুর আমাদের শুধু ইতিহাস শিখায়নি, আমাদের শেকড় চিনিয়েছে।”
সুদীপ্তর গলা একটু কেঁপে যায়। সে বলে, “আমার ঠাকুরদা একা ছিলেন না। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর প্রশ্ন, তাঁর পথ—সব আজ পূর্ণ হয়েছে। সেটাই উত্তরাধিকার। শুধুই রক্তের নয়, বিশ্বাসের।”
শেষ প্রদর্শনীর ফ্রেমে একটা ছবি ঝুলে থাকে—একটা পুরনো পাথরের সিন্দুক, পাশে লেখা:
“যারা ইতিহাসকে মরতে দেয় না, তারা চিরকাল বেঁচে থাকে।”
— সুবীর মুখোপাধ্যায়
আলো নেভে, কিন্তু গল্পটা থেকে যায়।
শেষ