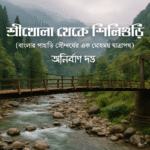অনির্বাণ দত্ত
পর্ব ১: পথচলার শুরু — শ্রীখোলার সকাল
পাহাড় মানেই যেন এক অনন্ত মুগ্ধতা। আর সেই মুগ্ধতা যদি হয় বাংলার বুকে — তাহলে তার আবেদনটা হয়ে ওঠে আরও গভীর, আরও আত্মিক। ঠিক তেমনই এক অনুভবের নাম শ্রীখোলা। দার্জিলিং জেলার প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রাম, যেখানে একটানা কুয়াশার চাদরে লুকিয়ে থাকে সূর্য, পাইন গাছের ছায়া পড়ে পাথুরে পথের উপর, আর ছোট ছোট পাহাড়ি নদী যেন গুনগুনিয়ে গল্প বলে। সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল আমার পথচলা — শিলিগুড়ির দিকে।
সকাল সকাল ঘুম ভাঙল পাখির ডাক আর নদীর শব্দে। শ্রীখোলার হোমস্টের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখা গেল কুয়াশার চাদর ঢাকা চারপাশের সবুজ পাহাড়। ছোট একটা কাঠের সেতুর নিচে ঝরনা বয়ে চলেছে, তার শব্দ এক অদ্ভুত শান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে মনে। সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, যেন কোনো এক বিস্মৃত রূপকথার জগতে পৌঁছে গেছি।
হোমস্টের মালিক, পরিতোষ দা, চা এনে দিলেন হাতে। কাঠের কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। তার গন্ধে যেন চা-পাতার পাশাপাশি মিশে আছে পাহাড়ি মাটি, বনফুল আর ঠান্ডা হাওয়ার গন্ধ। “বহুদূর যাবেন তো আজ?” পরিতোষ দা জিজ্ঞেস করলেন হাসতে হাসতে। মাথা নেড়ে বললাম, “হ্যাঁ, শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাবো। তবে তাড়াহুড়ো নেই।”
তিনি বললেন, “তাড়াহুড়ো না থাকলেই পাহাড় দেখা যায় ঠিক করে। এখানে সময় থেমে থাকে, আপনি শুধু অনুভব করুন।”
আমার ব্যাগ গোছানো ছিল আগেই। হাতে একটা ডায়েরি, একটা জলের বোতল, আর মনটা পুরোপুরি তৈরি। রওনা দিলাম হেঁটে হেঁটে, কারণ শ্রীখোলার প্রকৃতি হাঁটলেই বোঝা যায়, গাড়িতে নয়।
পথের শুরুতেই এক ছোট্ট ঝর্ণা পড়ল। পাথরের উপর দিয়ে জল গড়িয়ে নামছে, তার নিচে বুনো ফুল ফুটে আছে — লাল, বেগুনি, হলুদ। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে আমি হাঁটছি চুপচাপ, পাশে চলেছে সেই নদীটা — শ্রীখোলা নদী। নদীর নামেই এই গ্রামটির নামকরণ হয়েছে। “খোলা” মানে নদী বা স্রোত।চারপাশে নীরবতা, শুধু মাঝে মাঝে পাখির ডাক, কাঠবিড়ালির দৌড় আর হালকা বাতাসে পাতা নড়ে ওঠার শব্দ। এই নিস্তব্ধতা যেন কোনও তিব্বতী স্তোত্রের মতো, যার শব্দ নেই, কিন্তু সুর আছে।
শ্রীখোলা থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে গারিখোলা। পথটা বেশ খাড়া, তবে অসাধারণ। মাঝে মাঝেই ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। সেখানেই এক পাহাড়ি মহিলার সঙ্গে দেখা। তিনি এক ঝুড়ি ফুল নিয়ে যাচ্ছিলেন সান্দাকফু পথে, বিক্রি করার জন্য। হাসিমুখে বললেন, “শিলিগুড়ি যাচ্ছেন? ধীরে যান, পাহাড় তাড়াতাড়ি পছন্দ করে না।”
ওই কথাটা যেন সারা যাত্রার মন্ত্র হয়ে থাকল আমার কানে। গারিখোলায় পৌঁছে বিশ্রাম নিলাম একটু। নদীর ধারেই এক প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ রয়েছে। তার পাশে বসে মনে হল, সময় যেন এখান থেকে এগোয়নি অনেক বছর। পাথরের গায়ে লতানো গাছ, স্তূপের উপর লাল-হলুদ প্রার্থনাপতাকা, আর পাশে এক বৃদ্ধ লামা চুপচাপ বসে আছেন। এই শান্তি শুধু পাহাড় জানে।
পথে পথে পাইন গাছের সারি। সেই গাছের ফাঁকে মাঝে মাঝে কাঠের কুঁড়েঘর, কিছু জমিতে সিম লাগানো হয়েছে। শীতের শেষে এখানে চাষ শুরু হয়। বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে — তাদের পরনে নীল পোশাক, হাতে খাতা। এক ছোট্ট মেয়ে, তার নাম লাপচে, আমাকে বলল, “আপনি কি কলকাতা থেকে এসেছেন?” — আমি হেসে বললাম, “হ্যাঁ।” ওর চোখে ছিল বিস্ময়, যেন কলকাতা কোনও দূর দেশের গল্প। চলতে চলতে রোদ একটু একটু করে বাড়ছে। পেছনে তাকিয়ে দেখি, শ্রীখোলার মেঘ যেন ঢুকে পড়েছে আমার পেছনে আসা পথের মধ্যে। সে আর দেখা যাচ্ছে না। এখন শুধু সামনে পথ, আর আমি। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে ঢালুতে গাছপালা আর নীচে স্রোতস্বিনী নদী। হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখলাম — দূরে পাহাড়ের মাথায় রোদের ঝলক। ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে হল, আমি কোনও ছবির মধ্যে হাঁটছি।
পর্ব ২: রামমাম — ঝরনার শব্দে এক পাহাড়ি দুপুর
গারিখোলায় একটু বিশ্রাম নিয়ে যখন আবার হাঁটা শুরু করলাম, তখন সকাল গড়িয়ে প্রায় দুপুর। পেছনে শ্রীখোলা আর গারিখোলার ঘন সবুজ বনভূমি যেন রূপকথার পর্ব শেষ করে পেছনে রয়ে গেল। সামনে যে পথ, তা আরও খাড়া, আরও নির্জন — এবং হয়তো আরও রহস্যময়। চড়াই-উৎরাইয়ের এই পথে প্রকৃতি তার আরেক রূপ প্রকাশ করে। এখানকার বাতাস একটু বেশি ঠান্ডা, পাহাড়ের ঢালে এক ধরনের নীলচে ঘাস দেখা যায়, আর মাঝেমাঝে ছোট ছোট পাথরের গায়ে শেওলা জমে উঠেছে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় পথ ঢালু হয়ে নেমে গেল রামমামের দিকে — যেখানে পাহাড়ি ঝরনার শব্দ দূর থেকেই কানে এল।
রামমাম আসলে একটি ছোট্ট জনবসতি, আর তার আসল আকর্ষণ সেই বিখ্যাত ঝরনাটি — যার ধারে বসে পাহাড়ের প্রকৃত সৌন্দর্য হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। যখন পথ ক্রমশ পাথুরে হয়ে এল, তখন বুঝলাম কাছাকাছি চলে এসেছি। রাস্তার পাশে হঠাৎই একটি ছোট কাঠের দোকান পড়ে গেল। চা, বিস্কুট আর পাহাড়ি লোকেদের ব্যবহার্য কিছু জিনিসপত্র বিক্রি হয় এখানে। সেখানে দাঁড়িয়ে এক কাপ গরম চা খেলাম। দোকানদার বললেন, “এই পাহাড়ে যখন ঝরনা নামে, তখন সময় থেমে যায়।” এই কথার তাৎপর্য তখন বোঝা গেল না, কিন্তু রামমাম পৌঁছে বুঝলাম — তিনি কী বলতে চেয়েছিলেন।
ঝরনার সামনে দাঁড়িয়ে মন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন ধবধবে সাদা জলরাশি আকাশ থেকে নেমে আসছে, পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে গর্জে উঠছে। তার গায়ে রোদের আলো পড়ে তৈরি করছে ছোট ছোট রঙধনু। পাশে মোটা পাথরের উপর কিছু পর্যটক বসে আছেন, কেউ ছবি তুলছেন, কেউ চুপ করে বসে আছেন — আমার মতোই। আমি একটু আলাদা হয়ে ঝরনার একপাশে গিয়ে বসি। পাথরের উপর আমার ডায়েরি খুলে রাখি, কলম হাতে নিই, কিন্তু কিছুই লেখা হয় না। শুধু চুপ করে শুনি — সেই শব্দ। সে কোনো শব্দ নয়, যেন সময়ের স্রোত। শহরে যেখানে শব্দ কোলাহলে চাপা পড়ে যায়, এখানে তা এক বিশুদ্ধ ভাষা হয়ে ওঠে।
ঝরনার কাছেই এক পাহাড়ি ছেলে বসে ছিল, নাম লেকি। তার বয়স ১৪। সে জানাল, তাদের গ্রামে ইন্টারনেট নেই, বিদ্যুৎ মাঝেমধ্যে আসে, কিন্তু পাহাড়ের গল্প প্রচুর। সে বলল, “এই ঝরনার ধারে মাঝে মাঝে এক বুড়ো লামা আসতেন, বসে থাকতেন দিনের পর দিন। কেউ জানত না তিনি কী ভাবেন, কী বলেন। শুধু চুপ করে বসে থাকতেন। কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন।”
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “তিনি কি কিছু বলতেন কখনও?”
লেকি মাথা নাড়ল, “শুধু একবার বলেছিলেন, ‘যদি প্রকৃতি শোনো, তারাও কথা বলে।’”
এই কথাটা আমার মনে গেঁথে গেল। রামমাম থেকে যখন আবার হাঁটা শুরু করলাম, তখন দুপুর গড়িয়েছে। সূর্য একটু তীব্র, তবে পাহাড়ের ঠান্ডা বাতাসে তা একেবারে আরামদায়ক। এ পথ আরও সরু, মাঝে মাঝে পাথর খসে পড়েছে, তাই সাবধানে হাঁটতে হয়। চলার সময় পেছনে এক ঝলক ফিরে দেখলাম — রামমাম ঝরনার জলধারা নিচে গড়িয়ে যাচ্ছে, আর তার গায়ে পড়া রোদের ঝিলিক এখনও চোখে লেগে রয়েছে।
পথে একটি বাঁশঝাড় পড়ল। সেখানে এক বুড়ি মহিলা বসে ছিলেন। তিনি পাহাড়ি শালপাতায় মোড়া কিছু খাবার বিক্রি করছিলেন। আমি একটি কিনলাম — ভেতরে ছিল ‘থুংবা’ নামের এক ধরণের পাহাড়ি স্ন্যাকস, মোটা চালের তৈরি। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, “এখানে কেমন কাটে দিনগুলো?”
তিনি হেসে বললেন, “পাহাড়ে দিন চলে হাওয়ার সঙ্গে। সূর্য ওঠে, পাখি ডাকে, বৃষ্টি নামে — ব্যস, তাতেই জীবন।”
এ যেন পাহাড়ের দর্শন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই বুঝলাম, আজকের শেষ গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে। রামমাম থেকে তুমলিং রোডে ওঠার একটি ফাঁড়ি আছে — সেখান থেকে বাস বা জিপ পাওয়া যায় শিলিগুড়ির পথে নামার জন্য। তবে আমার ইচ্ছা ছিল যতটা সম্ভব হেঁটে যাওয়া। এক পর্যায়ে ক্লান্তি এসে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পাহাড়ের বাতাস যেন এক অদ্ভুত শক্তি দেয়। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক জায়গায় পৌঁছালাম, যেখানে এক চাতালে তিনটি চিরুনি রেখেছে কেউ — কাঠের তৈরি, তিনটি আলাদা আকারের। পাশেই একটি ছোট পাথরের স্তম্ভে লেখা, “তিন চিরুনির পথ — এখান থেকে তিনটা গল্প শুরু হয়।”
এই রহস্যময় চিহ্ন যেন জানিয়ে দিচ্ছিল, পাহাড়ের ভেতরে আরও কত গল্প লুকিয়ে আছে — যাদের খোঁজ আমি পাইনি।
বিকেলের শেষ আলোয় যখন পাইন বনের মধ্যে দিয়ে নামছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল — আজকের দিনটা যেন কোনও এক মহাকাব্যের প্রথম অধ্যায়। পাহাড় আমাকে তার মনের গোপন দরজা একটু খুলে দেখিয়েছে। ঝরনার শব্দ, ছোট্ট লেকির কথা, লামার নিঃশব্দতা — সব কিছু যেন একসাথে মিলেমিশে তৈরি করেছে এক ধ্যানের অভিজ্ঞতা। শেষে এক কাঠের সেতু পার হয়ে আমি পৌঁছালাম আরও একটি পাহাড়ি গ্রামে — যেটির নাম “কালাপোখরি”। এখানেই আজকের রাত কাটবে। কাল বৃষ্টি হলে হয়তো চলা বন্ধ থাকবে। কিন্তু পাহাড়ে সময় থেমে যায় না — সে শুধু ভাবে আর বলে — “ধীরে চলো, দেখো, শোনো, বাঁচো।”
পর্ব ৩: কালাপোখরি থেকে মিরিকের পথে — এক পাহাড়ি হ্রদের নীল নিঃশ্বাস
কালাপোখরি — একটি ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম, যার নামের মানে ‘কালো জল’। এখানে একটা হ্রদ আছে, যেটি ঠিক যেন আয়নার মতো শান্ত। কালো রঙের মতো গভীর, নির্জন ও আবেগময়। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এই জলাধার যেন এক বিস্ময়। রাতে যখন হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন তার গভীরতা ও নীরবতা আমাকে ঘিরে ধরেছিল — যেন নিজেকে নিজের চোখে দেখতে শিখছিলাম। এই হ্রদের পাড়েই ছিল একটি ছোট হোমস্টে। কাঠের তৈরি সেই বাড়িটা খুব সাধারণ, কিন্তু তার জানালা দিয়ে হ্রদের দৃশ্য দেখা যেত। রাতে কুয়াশার চাদরে ঢাকা পাহাড় আর সেই কালো হ্রদের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আমি বুঝেছিলাম — প্রকৃত নীরবতা শব্দের নয়, অনুভবের।সকালে ঘুম ভাঙল এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখে। জানালার বাইরে রোদের চিকচিকে আলো কুয়াশার পর্দা ভেদ করে পাহাড়ের গায়ে পড়ে যেন সোনালি রঙের ছোঁয়া দিয়েছে। হ্রদের জল এখনও অচঞ্চল, শুধু মাঝেমধ্যে একটি বা দুটি পাহাড়ি হাঁস সাঁতার কাটছে।
চা নিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসতেই, হোমস্টের দিদি বললেন, “আজকের দিনটা পরিষ্কার, ভালো করে দেখে যান কালাপোখরি।”
চা শেষ করে হ্রদের ধারে গেলাম। কাছাকাছি গিয়ে দেখি, হ্রদের জল একেবারে কালচে সবুজ। স্থানীয়রা বিশ্বাস করেন, এই হ্রদে একসময় এক তিব্বতি সাধু ধ্যান করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এ হ্রদের নিচে কোনও রহস্যময় গুহা আছে, যা নাকি এক পুরনো রাজবংশের ধ্বংসাবশেষ।
হ্রদের ধারে কিছুক্ষণ কাটিয়ে, আমি আবার হাঁটা শুরু করলাম। আজকের গন্তব্য মিরিক — পাহাড়ের আরেক বিস্ময়, একেবারে অন্যরকম মেজাজের শহর। কালাপোখরি থেকে মিরিক যেতে পাহাড়ি ট্রেইল ধরে যেতে হয়, আবার চাইলে জিপ ধরেও যাওয়া যায়। তবে আমি হাঁটতেই পছন্দ করলাম — কারণ পাহাড়ি পথের প্রতিটি বাঁকেই যে একেকটা গল্প লুকিয়ে।
পথে নেমে দেখি চারপাশে পাইন গাছের সারি। সূর্যের আলো পাতার ফাঁক গলে নিচে এসে এক অদ্ভুত আলোছায়ার খেলা করছে। হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় এসে থামলাম — পাথরের একটা পাড়ে ছোট্ট এক পাহাড়ি মেয়ে বসে গান গাইছে। সুরটি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু কণ্ঠে ছিল অদ্ভুত মাধুর্য।
আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কী গান?”
সে বলল, “এটা আমাদের মা বলতেন শৈশবে। এই পাহাড়কে আমরা মা বলি। তাই তার গল্পও গান হয়ে উঠে।”
যতোই পথ এগোয়, ততই পায়ের ওপর চাপ বাড়ে। কিছু কিছু জায়গা বেশ খাড়া, আবার কোথাও নিচের দিকে নামতে গিয়ে সাবধানে চলতে হয়। মাঝে মাঝে চুল্লু নামের পাহাড়ি মদ খেয়ে পর্যটকরা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে — এমনটা শুনেছি স্থানীয়দের কাছে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় এমন জায়গায় পৌঁছলাম, যেখানে দাঁড়িয়ে পুরো উপত্যকা দেখা যায়। নিচে এক ছোট নদী সাপের মতো এঁকেবেঁকে বয়ে যাচ্ছে, আর দূরের পাহাড়ে কিছু মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে — যেন স্বর্গীয় কোনো চিত্রকল্প। আমি পাথরের ওপর বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। এক বৃদ্ধ পাহাড়ি লোক পাশে এসে বসলেন। তার চোখে ছিল অভিজ্ঞতার ছাপ, গলায় ঝুলছিল এক প্রাচীন প্রার্থা মালা। তিনি হেসে বললেন, “আপনিও দেখছেন, তাই তো? এই পাহাড়ে যারা ভালোবাসে, তারাও পাহাড়ের সন্তান হয়ে ওঠে।”
আমি হাসলাম। সেই মুহূর্তে মনে হলো — হ্যাঁ, আমি এই পাহাড়ের সন্তান হতে চাই। দুপুর নাগাদ পথের পাশে এক চায়ের দোকান পড়ল। কাঠ ও টিন দিয়ে তৈরি ছোট দোকান, একদম পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। দোকানের পাশে কয়েকটা কাঠের বেঞ্চ, আর পিছনে এক পাহাড়ি বাগান। চায়ের অর্ডার দিয়ে বসে পড়লাম।
চা এল – ধোঁয়া ওঠা কড়া লাল চা, তার গন্ধেই যেন ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। দোকানের মালিক তামাক খাচ্ছিলেন, আর তার সঙ্গে ছিল এক কুকুর, নাম ‘ডোবা’। আমি চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, “মিরিক যেতে আর কতদূর?”
তিনি বললেন, “আর চার ঘণ্টার মতো হেঁটে গেলে পৌঁছে যাবেন। তবে হ্রদের কাছে পৌঁছনোর আগে বাঁশঝাড় পড়বে। সেখানে এক ঝরনার ধারে দাঁড়ালে আপনি বুঝতে পারবেন — পাহাড় কেমন করে মনকে ছুঁয়ে দেয়।”
তার কথা শুনে মনে হল, সে নিজেই কোনও কবি। দুপুরের পর আবার হাঁটতে শুরু করলাম। এবার পথ একটু সমান, কখনো ঢালু নিচে নেমে যাচ্ছে, আবার কখনো ঢুকছে ঘন বাঁশবনে। একসময় মিরিক শহরের প্রথম ঝলক চোখে পড়ল — দূর থেকে দেখা যায় বিশাল হ্রদের আভাস, তার একপাশে ছোট ছোট বাড়ি, আর অন্য পাশে পাইন-ঢাকা পাহাড়।
এই শহরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ মিরিক লেক, যাকে স্থানীয়রা বলেন সুমেন্দু লেক। এই লেক পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বিস্তৃত, আর তার ওপরে একটি বাঁশের সেতু — যেটা লেকের দুই প্রান্তকে যুক্ত করেছে। পাহাড়ের জলরাশি এখানে ঠিক যেন রূপকথার আয়না। লেকের ধারে বসে আমি হাঁপিয়ে পড়া শরীর নিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। চারপাশে অনেক পর্যটক, কিন্তু তারপরও মনে হচ্ছিল যেন একা — পাহাড়ের সঙ্গে একান্ত আলাপে মগ্ন। সন্ধ্যার সময় হ্রদের চারপাশে আলো জ্বলে উঠল। সাদা রঙের ছোট ছোট আলো, ঠিক যেন দীপাবলির আলো — তবে পাহাড়ের নিজস্ব ছন্দে। এক জায়গায় স্থানীয় ছেলেমেয়েরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছিল। বাঁশি, ধামসা আর পাহাড়ি ঢোলের সুরে এক অদ্ভুত আবহ তৈরি হল। আমি এক চা দোকানে বসে চা খেলাম। দোকানের পাশেই একটা পাহাড়ি কিশোরী ছবি আঁকছিল — মিরিক লেক আর পাইন গাছ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি কোথায় শিখেছো এঁকেছে?”
সে বলল, “এই পাহাড়ই আমার শিক্ষক। রোজ সকালে আমি এই হ্রদকে দেখি আর আঁকি।”
আমি বুঝলাম, পাহাড় শুধু শরীরকে না, মনকেও শুদ্ধ করে হ্রদের ধারে হোটেলটা ছিল ছোট কিন্তু সুন্দর। জানালা খুলতেই দেখা যায় লেকের জল, আর দূরের আলো। রাতে আমি হাঁটতে বের হলাম, পুরো মিরিক শহর যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু হ্রদের ধারে কিছু অল্প আলো আর নীরব জলরাশি।
চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে শুনলাম — পাহাড়ি বাতাসে কোথাও একটা বাঁশি বেজে উঠেছে। কে বাজাচ্ছে জানি না, হয়তো কোনও পাহাড়ি কিশোর, হয়তো সেই কল্পিত লামা — কিন্তু সুরটা মনে গেঁথে রইল। আজকের এই যাত্রা ছিল ক্লান্তিকর, কিন্তু মুগ্ধতার। কালাপোখরির গভীরতা থেকে মিরিকের সৌন্দর্য — সবই যেন এক কবিতা। পাহাড়ের পথ যেমন কঠিন, তেমনি সে হৃদয়ের কাছাকাছি। প্রতি বাঁকে সে এক নতুন গল্প বলে। রাত যখন গভীর, তখন মনে হল, আমি যেন নিজেকে এক নতুন করে খুঁজে পেয়েছি — পাহাড়ের প্রতিটি নিঃশ্বাসে, প্রতিটি হ্রদের ঢেউয়ে।
পর্ব ৪: মিরিক থেকে শিলিগুড়ি — বিদায়ের পথে শেষ পাহাড়ি আলিঙ্গন
পাহাড়ে বিদায় নেওয়া সবচেয়ে কঠিন কাজ। বিশেষত যখন পাহাড় নিজে আপনাকে আপন করে নেয়, তখন তার কোলে থেকে বেরিয়ে সমতলে নামার সময় বুকের ভেতর কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। মিরিক থেকে শিলিগুড়ির পথে সেই অনুভূতিই বারবার আমাকে গ্রাস করছিল। পাহাড়কে পেছনে ফেলে নামার প্রতিটি মুহূর্ত যেন বিদায়ের দীর্ঘশ্বাস।
সকালবেলা মিরিক লেকের ধারে চা খেতে খেতে ভাবছিলাম — “এখানেই যদি থেকে যাওয়া যেত কিছুদিন, পাহাড়ের বাতাসে নিজেকে ধুয়ে ফেলা যেত আরও একবার!” কিন্তু শহরের ডাকে ফেরা ছাড়া উপায় নেই। সেদিনই আমার ফেরার দিন। সকালটা ছিল হালকা মেঘলা। লেকের ওপর হালকা কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছিল, যেন পাহাড় নিজেই বিদায়ের আবছা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। হোটেলের বারান্দা থেকে দেখছিলাম পাইন গাছের সারি, নিচে সবুজ-নীল লেকের ঢেউ, আর দূরে পাহাড়ে ওঠা একফালি রোদ। হোটেলের দিদি এসে বললেন, “আজ চলে যাচ্ছেন? আবার আসবেন, পাহাড় ডাকবে।”
একটা হাসি দিয়ে বললাম, “ডাকে তো, কিন্তু আসা কি এত সহজ!”
চা শেষ করে ব্যাগ গুছিয়ে হোটেল ছাড়লাম। পিঠে ব্যাগ, হাতে হালকা একটি কোট — আর মনে একরাশ পাহাড়ি স্মৃতি।মিরিক থেকে শিলিগুড়ির দূরত্ব প্রায় ৫৫ কিলোমিটার। পাহাড়ি রাস্তা ধরে গাড়ি যেতে সময় নেয় প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। তবে যদি কেউ প্রকৃতি ভালোবাসে, তার কাছে এই রাস্তা নিজেই একটা গন্তব্য হয়ে ওঠে। আমি লোকাল শেয়ার জিপ ধরেছিলাম। জিপে আমার সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন স্থানীয়, এক ট্যুরিস্ট কাপল, আর এক বৃদ্ধ — যিনি পাহাড়ি গানে গলা মেলাচ্ছিলেন মনমোহা সুরে। জিপটা যখন পাহাড়ি রাস্তায় নামল, তখন সূর্যটা মেঘের ফাঁক দিয়ে লুকোচুরি খেলছে। দূরের পাহাড়গুলো ধীরে ধীরে পিছনে সরে যাচ্ছিল — যেন পাহাড় নিজেই বিদায় জানাচ্ছে আমাকে।
মিরিক থেকে নামতে নামতে যে দৃশ্যপট পাল্টে গেল, তা যেন সময়ের স্রোতের মতো। প্রথমে ছিল সবুজে মোড়া পাইন বন, যেখানে মেঘ আর সূর্যের খেলা; তারপর নেমে এল বাঁশঝাড়, চা বাগান, আর ছোট ছোট গ্রাম। পথে পড়ল সিমানা, এক পাহাড়ি মোড় যেখানে দাঁড়িয়ে দার্জিলিং জেলার শেষ টুকরোকে একবারে দেখা যায়। এখান থেকে তাকালে দূরের চা বাগানগুলো যেন সবুজ কার্পেটের মতো বিছানো। আমি জিপ চালককে বললাম, “দাদা, এক মিনিট দাঁড়ান তো।”
তিনি হাসলেন, “সবাই এখানেই একটু দাঁড়ায়। শেষবারের মতো পাহাড়কে দেখে নেয়।”
আমি দাঁড়িয়ে সেই সবুজের বিস্তার দেখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তটা চিরদিনের জন্য আটকে রাখতে চাই। যাত্রার মাঝপথে জিপ থামল এক পাহাড়ি চায়ের দোকানে। জায়গাটা নিরিবিলি, বাঁশ দিয়ে তৈরি সেই দোকানটির ছাদে রঙিন ঝালর ঝোলানো। চারপাশে কয়েকটা কাঠের বেঞ্চ, আর পাশে ছোট্ট ঝর্ণা। চায়ের অর্ডার দিয়ে বেঞ্চে বসে পড়লাম। পাশের বৃদ্ধ ভদ্রলোক কেশে উঠে বললেন, “পাহাড় ছেড়ে যাচ্ছেন?”
আমি বললাম, “হ্যাঁ, খুব ইচ্ছে করছে না যেতে।”
তিনি মাথা নেড়ে বললেন, “এখানে যারা একবার আসে, তারা চলে যায় ঠিকই, কিন্তু পাহাড় তাদের মন থেকে যায় না। এই রাস্তা ধরে ফিরবেন বারবার।”
চা এল — সোনালি রঙের, হালকা আদার গন্ধ। এক চুমুকেই মনটা হালকা হয়ে গেল। মনে হল, চা-ও পাহাড়ের মতো, অল্পতেই মায়া তৈরি করে। পথে পড়ল সুকিয়া পাহাড়ি — এখান থেকেই ধীরে ধীরে সমতলের ছোঁয়া পাওয়া যায়। এখান থেকে নিচে তাকালে পুরো তিস্তা ভ্যালি দেখা যায়। মেঘ এখানে আর পাহাড়ের গায়ে লেপটে নেই, বরং ওপরে উঠে যাচ্ছে।
আমি জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখছিলাম — পাখির মতো ভেসে বেড়ানো পাহাড়ি ঘরবাড়ি, চা বাগানের কাঁধ ঘেঁষে নামা কাঁচা পথ, আর মাঝে মাঝে বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে ইউনিফর্ম পরে। শেষ মোড়টায় এক বোর্ড লেখা ছিল — “শিলিগুড়ি ২৫ কিমি”।
মনটা খচ করে উঠল। বুঝলাম, এই যাত্রার শেষ পর্ব শুরু হয়ে গেছে। জিপটা যখন শিলিগুড়ির সীমান্তে ঢুকল, তখন সূর্য প্রায় পশ্চিমে হেলে পড়েছে। পাহাড়ি রাস্তা ক্রমশ সমান হয়ে গেছে, আর চারপাশে দেখা যাচ্ছে বাস, গাড়ি, বাইকের জটলা। এই শহর এখন আর পাহাড় নয়, বরং এক নতুন দিগন্তের মুখ। তবে মনটা বারবার পেছনে ফিরছিল — মিরিকের লেক, কালাপোখরির কুয়াশা, শ্রীখোলার স্রোত, আর পাইনবনের আলোছায়া।
শিলিগুড়ির বাসস্ট্যান্ডে নেমে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। এক ধারে বস্তার ওপর বসে এক পাহাড়ি যুবক বাঁশি বাজাচ্ছে। সুরটা কিছুটা পরিচিত — হয়তো মিরিকের সেই সন্ধ্যার সুর।আমি জানি, আবার আসব। আবার পাহাড় ডাকবে। আবার কুয়াশায় জড়ানো সকালে হাঁটব কোনও অজানা পথ ধরে। এই যাত্রা ছিল কেবলমাত্র ভ্রমণ নয় — ছিল আত্মঅন্বেষণের পথ। প্রতিটি পাহাড়ি বাঁক, প্রতিটি কুয়াশাঘেরা ভোর, প্রতিটি হ্রদের ধারে আমি নিজেকে নতুন করে চিনেছি।
শ্রীখোলা থেকে শিলিগুড়ি — এ এক গানের মতো যাত্রা। প্রকৃতির প্রতিটি স্তবক নিজস্ব ভাষায় কথা বলে গেছে আমার সঙ্গে। পাহাড় যেমন সবার হয় না, তেমনি যে একবার পাহাড়কে ভালোবেসে ফেলে, সে আর কখনও সত্যিই তাকে ভুলতে পারে না।
সমাপ্ত