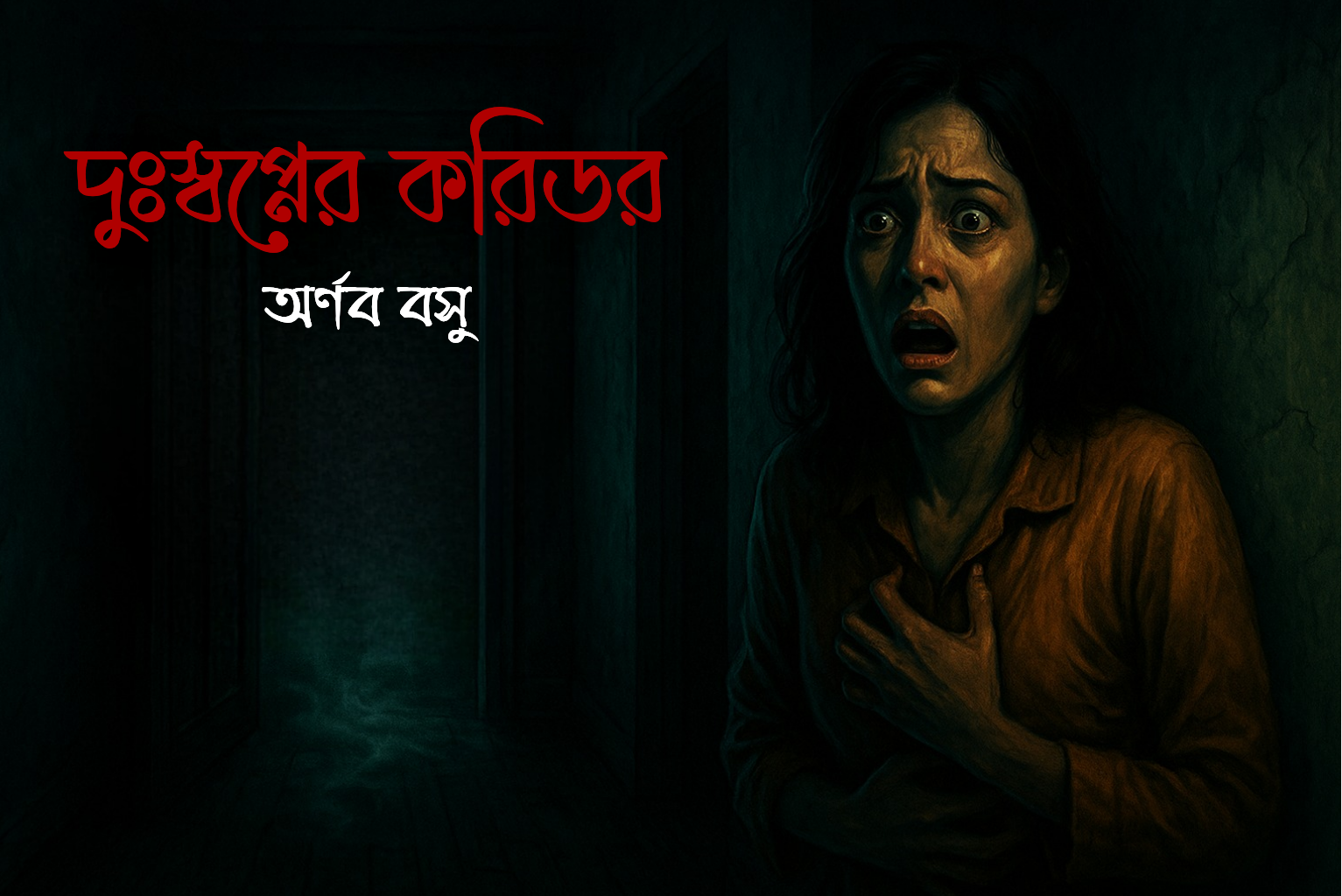রাতুল কোনার
ধুলেশ্বরীর সকাল
ধুলেশ্বরী গ্রামের সকালটা এককালে ছিল পাখির ডাক, লোনা হাওয়ার সুবাস, আর নারকেল পাতার ফিসফিসে কথার মধুর মিলনমেলা। এখন? এখন শুধু নোনাজলের ঝাঁঝ, ভাঙা কুঁড়েঘরের পাশে ছড়িয়ে থাকা বস্তার টুকরো, আর হঠাৎ হঠাৎ কাঁদা জমির বুকে ফুটে ওঠা লালচে ফাটল—যেন মাটির নিজস্ব হাহাকার।
জহর শেখ, পঁইত্রিশ বছরের জেলে, গামছা দিয়ে কাঁধ মুছতে মুছতে নৌকা ঘাটে পৌঁছল। চোখে-মুখে গভীর ক্লান্তি, আর একটা অপরাধবোধ—কাল রাতে সে ঘুমোতে পারেনি। সমুদ্রের ঢেউয়ের আওয়াজ, আর মাথার মধ্যে জমে থাকা দুশ্চিন্তার ঝড়—এই দুটোই তাকে ঘুমোতে দেয়নি।
তার ছেলে রায়হান, ক্লাস সেভেনে পড়ে, গতকাল বলছিল, “আব্বা, স্কুলে মাস্টার মশাই বলেছে, এইভাবে সমুদ্র বাড়তে থাকলে ধুলেশ্বরী ২০ বছরে ডুবে যাবে। ওরা বলে, ‘Sea Level Rise’। এটাই কী তাহলে আমাদের শেষ?”
জহর কিছু বলেনি, শুধু মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, “বাতাস যা বলে সব সত্যি না রায়হান। মাটি যদি না ছাড়ে, মানুষও ছাড়ে না।”
ঘাটে এসে দেখে তার নৌকার তলায় জমে আছে পলিমাটি। একসময় এই নদী, বগরা নদী, ছিল গ্রামের প্রাণ। এখন সেটা খেয়েছে নোনা জল, আর বর্ষায় নদীর জল উল্টো বেয়ে ঢুকে পড়ে ঘর-খেত সব ডুবিয়ে দেয়। জহর নৌকায় বসে, তলা থেকে কাদা বার করতে থাকে। তার মুখে চুনোপুঁটির মতো একটা নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস।
“জহর দা! শুনলেন তো কাল আবার ব্লক অফিস থেকে লোক আসছে জমি মাপতে?” — পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কুন্তলা চেঁচিয়ে বলে উঠল।
“জানি। ওরা বলে রিসর্ট হবে। অথচ আমাদের জল খাবার পাইপটাও ভাঙা পড়ে আছে মাসখানেক ধরে,” জহর বলল নিচু গলায়।
“তাও তো শুনেছি, ‘ধুলেশ্বরী ব্লু রিসর্ট’ নাম রাখবে! যেন কেউ আমাদের কষ্টের নীলজল দেখতে আসবে!” — কুন্তলা থুথু ফেলল পাশেই।
জহর আর কিছু বলল না। সে জানে, কুন্তলার ছেলেটা জ্বরে ভুগছে, সারা গ্রামে এখন ম্যালেরিয়া ফিরে এসেছে। আগে এমনটা ছিল না। বর্ষা এবার এলো না বলে, জমে থাকা নোংরা জলেই বংশবৃদ্ধি করছে মশা।
সে জানে, ধানক্ষেত ছিল তার মূল ভরসা। এখন সে একবছর ধান ফলায়, আর দুইবছর বানের জল পাম্প করে খাল থেকে সরাতে ব্যস্ত থাকে।
পেছনে, ঘরের ভাঙা বেড়া সরিয়ে বেরিয়ে এল জহরের স্ত্রী হাসিনা। তার চোখে ক্লান্তি, হাতে কাঁথা ঝাঁট দেওয়া কাপড়।
“এই নাও, তোমার জালে ছেঁড়া ধরেছে। আমি সেলাই করে দিয়েছি।”
জহর সেই ভেজা জাল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। এই জাল যেন তার জীবনেরই প্রতিরূপ—পুরনো, ফাটা, বারবার সেলাই করা।
“বড় মাছ উঠে না এখন, হাসিনা। আগে একবার খেপে তিন কুন্তাল ইলিশ উঠত। এখন তো খেপে খেপে পুঁটি আর বাইম ছাড়া কিছুই পাই না।”
“কী করবে তুমি একা? প্রকৃতি রাগ করেছে, আমরা তো শুধু সহ্য করি,” — হাসিনা বলল শান্তভাবে।
রায়হান তখন খোলা উঠোনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির অপেক্ষায় ছিল। তার হাতে ছিল স্কুলব্যাগ, আর চোখে ছিল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা একরাশ প্রশ্ন।
“আব্বা, মাস্টারমশাই বলেছে, আমরা যদি গাছ না লাগাই, তাহলে বাতাস মরবে। কিন্তু আমাদের তো জায়গাই নেই গাছ লাগাবার!”
“তা ঠিক। তবে ছোট জায়গাতেও বড় কাজ হয়। যে মাটিতে গাছ একবার বাঁচে, সে মানুষকেও বাঁচায়,” — জহর বলল।
হাসিনা হঠাৎ বলল, “কাল রাতের ঝড়টা কি একটু বেশি ছিল না? চালার ওপরে তো একটা টিন উড়ে গেল আবার।”
জহর মাথা নেড়ে বলল, “হ্যাঁ, আগের মতো ঝড় আসে না, এখন ঝড়ের বুকের মধ্যে আগুন থাকে। মনে হয়, আকাশের রাগ যেন কেবল আমাদের ওপরই পড়ে।”
গ্রামের মসজিদ থেকে আজান ভেসে আসছিল। সকাল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। জহর আবার নৌকায় চেপে বসল, জাল নিয়ে পাড়ি দিল নদীর দিকে। মাছ কমে এসেছে, কিন্তু সে জানে খুঁজতে হবে। না হলে চুলায় হাঁড়ি চড়বে না।
নদীর মাঝখানে এসে সে একটু দাঁড়াল। বগরা নদী, যাকে সে ছোটবেলা থেকে মা বলে মেনে এসেছে, এখন যেন এক নি:শব্দ অথচ ভয়ংকরী নারী, কেবল নিয়ে যাচ্ছে—ফিরিয়ে দিচ্ছে না কিছুই।
তবু জহর জানে, তাকে ফিরতে হবে।
এই ধুলেশ্বরীই তার ঘর, তার ভিটে, তার জীবন। মাটি ফেটে গেলেও, মানুষ যদি তাতে পা রাখে, সেই মাটি আবার নিজের করে নেয়।
মৌসুমি ব্যাধি
বৃষ্টি এখন আর ঠিক সময়ে আসে না। একসময় আষাঢ়-শ্রাবণে যে বৃষ্টি হতো সে যেন এখন এসে পড়ে কার্তিক বা মাঘের শেষে। ধুলেশ্বরীর পুরনো কৃষক নিত্যানন্দ ঘোষ প্রতিদিন খেতের আইলের পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ধানের গাছগুলো শুকিয়ে বাদামি হয়ে গেছে। চারা লাগানোর সময়সীমা পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই, অথচ একফোঁটা জলের দেখা নেই।
“আগে চার মাস আগেই জমি ভিজে যেত। এখন ছয় মাসেও কাদা হয় না,” নিত্যানন্দ বললেন জহরকে, “জল না থাকলে ধান হবে কেমন করে বলো!”
জহর ঘাড় নাড়ল। সে জানে, নদীতে নোনা জল ঢুকে পড়ে, তাই সেচের খালগুলোও নোনতা হয়ে গেছে। সেই জল দিয়ে ধান চাষ করলে গাছ পঁচে যায়।
গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নতুন করে রোগী ভিড় জমিয়েছে। জ্বর, কাশি, পেট খারাপ—এখনকার ধুলেশ্বরীর নতুন অচেনা চেহারা। রোগগুলো যেন আগেও ছিল, কিন্তু এখনকার মতো ভয়ানক ছিল না কখনও।
ডাক্তার শুভদীপ মণ্ডল, গ্রামের নতুন তরুণ ডাক্তার, একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, “এই যে বারবার জল জমে থাকে বাড়ির চারপাশে, সেটা মশার আঁতুড়ঘর। কিন্তু লোকজন কেউ কানে তোলে না।”
তিনি জানালেন, গত তিন সপ্তাহে ২৩ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। এরমধ্যে ৮ জন শিশু। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইনজেকশন আর ওষুধের সরবরাহও শেষ হতে চলেছে।
“ডাক্তারবাবু, আমার মেয়েটা কিছু খাচ্ছে না,” — বলল লতিকা, চোখ ভরা জল নিয়ে, “জ্বর কমছে না, গায়ে ফোসকা উঠেছে।”
শুভদীপ ভ্রু কুঁচকে বললেন, “এটা ডেঙ্গুও হতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা করানোর মতো ব্যবস্থা এখানে নেই। আপনাকে নদীয়া হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।”
“কিন্তু স্যার, ওখানে তো যেতে তিনশো টাকা ভাড়া পড়ে। আমার কাছে এখন একশো টাকাও নেই,” — লতিকা ফুঁপিয়ে উঠল।
শুভদীপ চুপ করে রইলেন। তিনি জানেন, ধুলেশ্বরীর মতো শত শত গ্রাম এভাবেই মৌসুমি রোগের কবলে পড়ে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এসব কথা প্রশাসন জানতে চায় না, মিডিয়া তো নয়ই।
একদিকে যখন অসুখ ছড়াচ্ছে, অন্যদিকে দূষণ বাড়ছে দিনের পর দিন। গ্রামে রাস্তাঘাট বলতে কাঁচা মাটির পথ। পাশের নদীর পাড় দিয়ে বয়ে যাওয়া ড্রেন এখন একটাই নাম পেয়েছে— “প্লাস্টিক ঝরনা”। মুড়ির প্যাকেট, চিপসের খোসা, সস্তা শ্যাম্পুর বোতল—সবকিছু এসে জমে নদীর মুখে।
কুন্তলা বলল, “আগে নদী থেকে জল আনতাম রান্নার জন্য। এখন একবার চামচ ঢুকালেই উঠে আসে কালো পিচপিচে কিছু একটা।”
জহর জানে, এই প্লাস্টিক দূষণ শুধু নদী নয়, জমিও মারছে। চাষের জমিতে জল যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর সরকার যেসব সোলার পাম্প বসিয়েছে, সেগুলো ২-৩ মাসের মধ্যে বিকল হয়ে পড়ে আছে।
রাতের বেলা, ঘরের মধ্যে চারদিকে মশার ঝাঁক। রায়হান খুপরি খুপরি কাশছে।
“এই কাশিটা তো পাঁচদিন ধরে। জ্বর ছিল না?” — জিজ্ঞেস করল জহর।
“ছিল, তবে কমে গেছে এখন,” রায়হান বলল।
হাসিনা ওর কপালে হাত দিয়ে বলল, “আবার বাড়ছে না তো?”
জহর জানে, এমন হলে রায়হানকে কলকাতা পাঠাতে হতে পারে। তার খরচ সে কেমন করে বহন করবে?
“বাবা, মাস্টারমশাই বলছিলেন, এখন যেসব রোগ হচ্ছে, সেগুলোর অনেকগুলোর কারণ হল আবহাওয়ার পরিবর্তন। আগে এটা হতো না।”
“তা তো ঠিক,” — জহর বলল, “প্রকৃতি বদলালে রোগও বদলায় রায়হান।”
পরদিন সকালে জহর আর নিত্যানন্দ একসাথে গেল বাঁধ দেখতে। বর্ষার জল ধানক্ষেতে না ঢুকে যাতে নদীর খালে চলে যায়, সেইজন্য একটা ছোট মাটির বাঁধ করা হয়েছিল। এখন সেটা ধসে গেছে। জল এসে পেছনের পাঁচটা জমি ভিজিয়ে দিয়ে গেছে। সেখানে এখন ধান তো নয়, কেবল নোনাজলের শৈবাল।
“এই জমি এবার আর কাজে লাগবে না,” — বলল নিত্যানন্দ, “আকাশে মেঘ নেই, মাটিতে জল নেই—এটাই কি কৃষকের ভবিষ্যৎ?”
জহর শুধু বলল, “এখন কৃষক আর জেলে এক কাতারে, কেবল ভাগ্যেই ভরসা।”
সন্ধেবেলা ডাক্তার শুভদীপ ও কুন্তলা একটা ছোট সভা ডাকলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে।
“আমরা চাই সবাই যেন অন্ততপক্ষে বাড়ির পাশে জল না জমতে দেয়,” — বললেন শুভদীপ, “সবার বাড়ির সামনে একটু করে গর্ত খুঁড়লে, জল সরে যাবে। আর অন্তত একটা করে নিমগাছ লাগাতে পারলে মশার পরিমাণ কমবে।”
কেউ কেউ মাথা নাড়ল, কেউ কেউ চুপ।
জহর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “ডাক্তারবাবু ঠিকই বলছেন। আমরা যদি নিজের গ্রামকে না বাঁচাই, বাইরের লোক এসে কিছু করবে না। আমি কাল সকালেই আমার বাড়ির পাশে গর্ত করব।”
একটু ফিসফাস শুরু হলো, কেউ বলল, “তবু তো সরকার কিছু করে না, শুধু আমরা করলে কী হবে?”
জহর বলল, “জল বাড়লে সবাই ডুবে। তাই আগে নিজের খুঁটি ঠিক করতে হয়।”
রাতে, তার ঘরে ফিরে জহর জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ। নীচে রায়হান ঘুমোচ্ছে, পাশে হাসিনা নিঃশব্দে শুয়ে।
মাথার উপর নক্ষত্রহীন আকাশ, আর বুকে উপচে পড়া একরাশ অসহায়তা।
তবু জহর জানে—একটা কিছু করতেই হবে।
প্রকৃতি যতই বিরূপ হোক, প্রতিরোধের শুরুটা হতে হয় মাটির কাছ থেকে। আর মাটি কখনও নিজের সন্তানকে পরিত্যাগ করে না, যদি সে সন্তান ফিরে এসে তার কোল আঁকড়ে ধরে।
জল উঠে এলো
সেই রাতে আকাশ যেন হঠাৎ চিৎকার করে উঠল।
বিকেল থেকেই আকাশের মুখ ভার ছিল। কিন্তু গ্রামের মানুষজন এমন দমকা হাওয়া ও ছুটন্ত মেঘ দেখে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল গত কয়েক বছর ধরে। আগের মতো আর কেউ আকাশ দেখে ভবিষ্যৎ বলে না, কারণ এই আকাশ নিজেই এখন আর নিজের কথা মানে না।
তবুও, রাত আটটার পর যখন দক্ষিণ দিক থেকে এক অদ্ভুত গর্জন ভেসে এলো, তখন ধুলেশ্বরী থমকে গেল।
“ঝড় আসছে!” — চেঁচিয়ে উঠল কুন্তলা। “ঘূর্ণিঝড়! সাইক্লোন! খবর লাগাও, সবাইকে খবর দাও!”
বেতারওয়ারলেস বলছিল, “ঘূর্ণিঝড় ‘অগ্নিবীণা’ উপকূল বরাবর স্থলভাগে আঘাত হানতে চলেছে। গতিবেগ ১০০-১২০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা।”
জহর তখন নদী থেকে ফিরছে। হঠাৎ মাঝ নদীতে ঢেউয়ের মুখে পড়ে সে কোনওমতে নৌকা টেনে এনে ঘাটে বাঁধল। চাঁদের আলো নেই, বাতাসে লোনা জলের ছিটা তার চোখে, মুখে, কাঁধে কেটে বসছে।
“হাসিনা! রায়হান কোথায়?” — ঘরে ঢুকেই সে হাঁক দিল।
“ও ঘুমাচ্ছে, কিন্তু বাইরে বাতাসে জানালা খুলে গেল। আমি চট দিয়ে ঢাকতে গিয়েছিলাম।”
জহর একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে জানালা গুঁজে বেঁধে দিল। বাইরে বাঁশগাছগুলো বেঁকে গেছে, তালপাতার ঝাঁকড়া ছাদ টিনে টিনে ধাক্কা খাচ্ছে।
গ্রামের কেন্দ্রের পুরোনো বটগাছটাও অদ্ভুতভাবে দুলে উঠছে — যেন তার শিকড়গুলো আর মাটি আঁকড়ে রাখতে পারছে না।
রাত ৯টার দিকে পুরো গ্রামে বিদ্যুৎ চলে গেল। মোবাইলের সিগন্যালও ভোঁতা। কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই। কেবল বাতাসের গর্জন আর গাছপালার ভাঙচুর শোনা যাচ্ছে।
ঠিক সেই সময় হঠাৎ খবর এল—পূর্ব দিকের বাঁধ ভেঙে গেছে।
কুন্তলার বাড়ি বাঁধের কাছেই। সে তখন কোমর জলে দাঁড়িয়ে ছেলের হাত ধরে দৌড়াচ্ছে। তার গলা ফাটছে, “বাঁচাও! কেউ বাঁচাও!”
একজন যুবক এগিয়ে গিয়ে বলল, “এইদিকে, স্কুলঘরের দিকে চলুন! ওখানে উঁচু জমি আছে!”
দশ মিনিটের মধ্যে গ্রামের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায়। ঘরবাড়ি, খেত, টিউবওয়েল—সব ডুবে গেল। বৃষ্টির কোনো স্পষ্ট শব্দ নেই, কেবল হাওয়ার মধ্যেই যেন জল ছিটকে পড়ছে, তীব্রভাবে, আঘাতের মতো।
জহরের ঘরও একসময় কাঁপতে শুরু করল। হাসিনা চেঁচিয়ে উঠল, “টিনটা খুলে গেল! আর পারছি না!”
জহর মাটিতে পড়ে থাকা একটা পুরনো খাটিয়া এনে ছেলের মাথার ওপরে ধরল।
“বাবা, আমার গা জ্বালছে,” — বলল রায়হান। তার শরীর তখনও কাঁপছে। মনে হচ্ছিল তার জ্বর বাড়ছে। এমন দুর্যোগে চিকিৎসা তো দূরের কথা, একটা শুকনো কাপড় নেই ওকে মুড়ানোর মতো।
রাত ২টার দিকে পানি এসে তাদের উঠোনে ঢুকল। জহর জানত, সময় শেষ। সে হাসিনার হাত ধরল, রায়হানকে কোলে নিল, আর বেরিয়ে পড়ল অন্ধকারের ভিতর।
গ্রামের স্কুলঘর ছিল একমাত্র পাকা বিল্ডিং। সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিল প্রায় ৪০-৫০ জন মানুষ।
শুভদীপ ডাক্তার সবার জন্য ওষুধপত্র জোগাড় করে রেখেছিলেন, যতটুকু পেরেছিলেন। তিনি দেখছিলেন, বেশ কিছু শিশু কাঁপছে, কেউ কেউ কাঁদছে জ্বর আর ভয়ে।
কুন্তলা বলল, “রায়হান এসেছে?”
জহর তখনও আসেনি।
একসময় দরজায় ভিজে চেহারায় জহর এসে দাঁড়াল। কোলে তার ছিল নিস্তেজ রায়হান।
“ডাক্তারবাবু! রায়হান কিছু বলছে না…জ্বর গায়ে গরম হয়ে গেছে,” — জহরের কণ্ঠে হাহাকার।
শুভদীপ তাকে শুইয়ে পরীক্ষা করলেন। চোখে আলো ফেললেন, গায়ে গরম পট্টি চাপালেন।
“জ্বর বেড়েছে, প্রচণ্ড। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এখানে অক্সিজেন নেই,” — তিনি বললেন।
“কী করব ডাক্তারবাবু! কোথায় যাব?” — কেঁদে উঠল হাসিনা।
শুভদীপ চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, “একটাই উপায়—ভগবান এখন যা চান…”
সকাল হলে, ঝড় কিছুটা কমে এল। কিন্তু ধুলেশ্বরী যেন এক যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ভূখণ্ড। গাছ উপড়ে গেছে, নদীর পাড় হঠাৎ এক কিলোমিটার ভিতরে চলে এসেছে। পুরনো বাঁধ নামক একটা শব্দই আর নেই।
অনেক ঘরবাড়ি গিয়েছে, অনেক মানুষ নিখোঁজ। তাদের মধ্যে একজন—রায়হান।
জহর তাকে কাঁধে করে স্কুল থেকে নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছিল, পথে হঠাৎ একটা ভাঙা নারকেলগাছ এসে পড়ে।
সেই ঝাঁকুনিতে তার হাত থেকে ছুটে যায় ছেলেটা।
জহর অন্ধকারে বারবার পানিতে হাতড়েছে, চেঁচিয়েছে, কেঁদেছে।
কিন্তু রায়হান আর ফেরেনি।
সকাল ৮টা নাগাদ সূর্য উঠেছে, কুয়াশার মতো নোনা হাওয়া বইছে। জহর বসে আছে নদীর ঘাটে, খালি হাতে।
সে চুপচাপ নদীর দিকে তাকিয়ে আছে, যেন নদী কিছু বলবে।
তাকে কেউ ডাকছে না, কেউ সান্ত্বনা দিচ্ছে না। কারণ সবাই জানে, যার ছেলে হারায়, তার কান্না বাইরের কেউ বুঝতে পারে না।
এখন ধুলেশ্বরী শুধু একটা ভাঙা গ্রামের নাম নয়—এটা একটা প্রশ্ন।
প্রশ্নটা দাঁড়ায় এইভাবে: যদি প্রকৃতি এতটা প্রতিশোধপরায়ণ হয়, তবে আমরা কি কেবল সহ্য করেই যাব?
নাকি আমরা প্রতিরোধের পথ খুঁজব?
এ প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা। কিন্তু জহরের চোখে তখন কেবল একটাই কথা লেখা—”এবার কিছু করতেই হবে।”
পর্যবেক্ষকের আগমন
কলকাতার বেলভিউ কলেজের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক রীমা ব্যানার্জী প্রথম যখন ধুলেশ্বরীতে পা রাখলেন, তখন চারদিক যেন চুপচাপ।
মনে হচ্ছিল, একটা গোটা গ্রাম নিঃশব্দে শ্বাস নিচ্ছে। গাছগুলো যেন কথা বলছে না, আর পাখিরা হয় উড়ে গেছে, না হয় হারিয়ে গেছে চিরতরে।
রীমা একটি গবেষণা প্রকল্পে কাজ করছেন—বাংলার উপকূলবর্তী এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা, বিশেষ করে জনজীবনে তার প্রতিক্রিয়া।
সাথে ছিলেন একজন সহকারী, অভিক ঘোষ, এবং স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি সুজাতা পাল।
“এই তো ধুলেশ্বরী,” সুজাতা বললেন, “আগে নদী ছিল অনেক দূরে। এখন ঘরের উঠোনে আসে জল।”
রীমা সাদা চামড়ার মতো একটা ছোট ডেটা রেকর্ডার বের করে মাটি থেকে আর্দ্রতা, তাপমাত্রা মাপছিলেন।
“দেখুন অভিক, এখানে নোনাজলের উপস্থিতি এতটাই বেশি যে ধানের বীজ বাঁচে না। আর সেই কারণে খাদ্য সংকট প্রকট।”
অভিক নোট নিচ্ছিল, ছবি তুলছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত বাঁধের, পানিতে ডুবে থাকা মাঠের, আর জর্জরিত মানুষের মুখের।
প্রথম দিনেই তারা গিয়ে পৌঁছাল স্কুলঘরে, যেখানে ঘূর্ণিঝড়ের সময় মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল।
ডাক্তার শুভদীপ এসে বললেন, “আপনারা যদি সত্যিই কিছু করতে চান, তাহলে আমাদের একটা ক্লিনিক তৈরি করে দিন। সামান্য জ্বরেও মানুষ মারা যায় এখানে।”
রীমা হাসলেন না, শুধু বললেন, “আমরা রিপোর্ট জমা দেব কেন্দ্রীয় ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্স ফান্ডে। তবে হ্যাঁ, কথা দিয়ে কিছু হবে না। আমি চাই তথ্য, এবং আপনারা যদি আমাদের সাহায্য করেন, তাহলে সেই তথ্য উঠে আসবে।”
কুন্তলা বলে উঠল, “তথ্য দিয়ে কী হবে? রায়হান তো ফিরবে না।”
সবার মুখ থেমে গেল।
জহর তখন পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে এগিয়ে এসে বলল, “তথ্য যদি কারও ভবিষ্যৎ বাঁচাতে পারে, তাহলে দেরি করা চলবে না। আমি সাহায্য করব।”
রীমা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনিই জহর?”
জহর হালকা মাথা নাড়ল।
“আপনার কথা আমরা আগেই শুনেছি সুজাতার কাছ থেকে। আপনি কি আমাদের গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন?”
“চলুন,” জহর বলল।
তারা প্রথমে গেল পূর্ব পাড়ায়, যেখানে বাঁধ ভেঙে পুরো পাঁচটা জমি জলমগ্ন হয়ে আছে।
রীমা দেখে নিলেন জমির উপরিভাগে জমে থাকা নোনাজল, তার নিচের স্তরে থাকা কালো কাদা, আর উপচে পড়া শৈবালের ঘনত্ব।
“এই জায়গায় আর কিছু জন্মাবে না,” তিনি বললেন।
“জমি মরে গেল?” — অভিক প্রশ্ন করল।
“জমি নিজে মরে না। আমরা তাকে মেরে ফেলি। আর যদি জীবিত রাখতে চাই, তাহলে তাকে নতুনভাবে তৈরির পথ খুঁজতে হবে। বায়ো-রেমিডিয়েশন, রেইনওয়াটার হারভেস্টিং, সল্ট রেসিস্ট্যান্ট ক্রপ—সব ভাবতে হবে।”
রাতে, স্কুলঘরের বারান্দায় বসে রীমা জহরের সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন।
“আপনার ছেলে… রায়হান… আমি শুনেছি,” — তিনি বললেন আস্তে।
জহর কিছু বলল না, কেবল চোখ মেলে তাকিয়ে থাকল নদীর দিকে।
“আমি জানি, আমার দেখা-শোনা আর গবেষণা আপনার ক্ষতিকে ফেরাতে পারবে না। কিন্তু আমি যদি এই গ্রামের গল্পটা বড় করে তুলতে পারি, তাহলে হয়তো এটার জন্য একটা লড়াই শুরু হবে।”
জহর বলল, “লড়াই আমরা তো করেই যাচ্ছি। কিন্তু যদি আপনারা পাশে থাকেন, তাহলে এটা শুধু বেঁচে থাকার লড়াই হবে না, বদলের লড়াইও হবে।”
পরদিন তারা সবাই মিলে গ্রামের মানুষদের নিয়ে একটি ছোট সভা করল।
রীমা বোঝালেন কীভাবে স্থানীয়দের নিয়ে তৈরি করা যায় ‘কমিউনিটি ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ’।
সুজাতা বললেন, “আপনারা নিজেরাই যদি পুকুর খনন, বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা, এবং প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা হাতে নেন, তাহলে আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়াব।”
“কিন্তু চারা, যন্ত্রপাতি, টাকা কোথা থেকে আসবে?” — জিজ্ঞেস করল নিত্যানন্দ ঘোষ।
“আমরা আবেদন করব ‘জলবায়ু অভিযোজন তহবিলে’। তবে আপনারা কাজ শুরু করে দিন। সময় নষ্ট করলে প্রকৃতি আর সময় দেবে না,” — রীমা বললেন।
অন্তিমে, যখন তারা ফিরে যাচ্ছিলেন, রীমা একবার থেমে নদীর দিকে তাকালেন।
নদী তখন শান্ত, ছলছল করছে সূর্যের আলোয়।
তবুও রীমা জানতেন, এই শান্ত জল যেকোনও দিন আবার জেগে উঠতে পারে। কিন্তু এবার যদি মানুষ আগেভাগেই প্রস্তুত থাকে, তাহলে ধুলেশ্বরীকে শুধু “একটি ডুবে যাওয়া গ্রাম” হিসেবে ইতিহাসে লেখা হবে না।
এটা হতে পারে এক “জেগে ওঠার গল্প”।
সবুজের খোঁজে
শীত আসতে না আসতেই ধুলেশ্বরীর হাওয়া বদলাতে শুরু করল।
এবার আর শুধু বাতাস নয়—মানুষের মনেও যেন এক নতুন জাগরণ বয়ে যাচ্ছিল।
রীমা কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন, কিন্তু তার রেখে যাওয়া সেই চার পাতার রিপোর্ট আর একটা ছোট সাদা বোর্ড স্কুলঘরের গায়ে এখনও টাঙানো।
বোর্ডে লেখা:
“জলবায়ু অভিযোজন শুরু হোক গ্রামের ভেতর থেকেই।”
এক ভোরে জহর, কুন্তলা, শুভদীপ আর আরও কয়েকজন মিলে গ্রামের শ্মশানঘাটের পিছনের খালি জমিতে গিয়ে দাঁড়াল।
জমিটা আগে ছিল খেত, তারপর ভেঙে গিয়ে নোনা জল জমে সেখানে কিছুই আর জন্মাত না।
“এইখান থেকে শুরু করব,” — জহর বলল।
“কীভাবে? চাষ তো হবে না!” — নিত্যানন্দ সন্দেহ করল।
“রীমাদি বলেছিল একটা কথা—সবুজ ফিরলে জলও পালটে যাবে। মানে গাছ লাগালেই শুধু ছায়া নয়, মাটিও শক্ত হবে, আর হাওয়াও ঠান্ডা থাকবে। পুকুরের জল কম নোনতা হবে,” — শুভদীপ ব্যাখ্যা করল।
সুজাতা তখন নিয়ে এল এক গাদা চারা গাছ—সোনাঝুরি, মেহগনি, নিম আর খেজুর।
“এই গাছগুলো নোনাজলে বাঁচতে পারে। সাঁতরা কলেজের নার্সারি থেকে এনেছি,” — সে বলল।
দিনটা ছিল শুক্র, সবাই অর্ধদিন কাজ শেষে চলে এলো।
পিঠে কোদাল, হাতে বাঁশের মুগুর, মাথায় পুরনো টুপি পরে কুন্তলা নিজেই কাদা মেখে গাছ পুঁততে শুরু করল।
“দ্যাখো গো, রায়হানের নামেই এই গাছটা লাগাচ্ছি,” — সে বলল।
হাসিনা আস্তে এসে দাঁড়াল, কাঁদল না, শুধু মাথা নিচু করল।
“এই গাছগুলো রায়হানের জন্যও,” — সে বলল।
জহর তখন একটা খেজুরগাছ পুঁতে বলল, “এই গাছটা যার ছায়ায় বড় হবে, সে যেন রায়হানের মতো সাহসী হয়।”
পরের কয়েক দিনে স্কুলের বাচ্চারাও হাত লাগাল।
একদিন দেখা গেল ছোট্ট অনন্যা একটা প্লাস্টিকের বোতলে জল এনে গাছের গোড়ায় দিচ্ছে।
“কে বলল তোকে?” — জিজ্ঞেস করল কুন্তলা।
“শিক্ষক বলেছে, গাছ বাঁচলে আমরা বাঁচব। আমার মা বলে, এখন দুধের থেকেও জল দামী।” — ছোট্ট মেয়ে মাথা নাড়িয়ে বলল।
একটা জায়গায় পুকুর খননের কাজ শুরু হল।
পুরোনো ভরাট পুকুরের গায়ে কোদাল চালিয়ে মাটি তোলা শুরু করল জহর আর আরও তিনজন।
পুকুরে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা হবে, যাতে বর্ষায় আবার জল জমে গ্রামের মধ্যে না ঢোকে।
সুজাতা জানাল, “সরকারি প্রকল্পে ‘পর্যায়ক্রমিক জলসঞ্চয়’ নামে একটা নতুন ফান্ড এসেছে। আমরা চেষ্টা করব ধুলেশ্বরীর নামে একটা আবেদন জমা দিতে।”
এই সময়েই, শুভদীপ একটা নতুন ভাবনা নিয়ে এল।
“আমাদের এখানে একটা শিশু শিক্ষাকেন্দ্র দরকার। স্কুল তো আছে, কিন্তু পরিবেশ নিয়ে কিছু শেখানো হয় না।”
“তুমি ভাবছ কীভাবে?” — কুন্তলা জিজ্ঞেস করল।
“রবিবারে এক ঘন্টা করে আমি ক্লাস নেব। বাচ্চাদের জল, বাতাস, গাছ আর রোগ-বালাই সম্পর্কে সচেতন করব। জানো, অনেকেই জানে না প্লাস্টিক পুড়িয়ে দিলে কী গন্ধ হয়, আর সেটা শরীরে কত বিষ ঢোকে।”
“তা হলে ওই ক্লাসের নাম দাও ‘জলপাঠশালা’,” — হাসিনা বলল হঠাৎ।
সবাই একসাথে হেসে উঠল। নামটা ঠিক হয়ে গেল।
একদিন বিকেলে, অভিক ফিরে এল। হাতে একটা ছোট ক্যামেরা, কাঁধে সোলার পাওয়ার প্যানেল।
“রীমাদি বলেছে গ্রামের একটা ভিডিও রিপোর্ট বানাতে। ফান্ড পেতে এগুলো কাজে লাগবে,” — সে বলল।
অভিক ঘুরে ঘুরে চাষিরা কীভাবে মাটি তৈরি করছে, বাচ্চারা কীভাবে গাছকে জল দিচ্ছে, সেটা ক্যামেরায় ধরতে লাগল।
একটা মুহূর্তে সে থেমে গেল—এক পুরোনো নারকেলগাছের নিচে জহর বসে আছে, পাশে ছোট্ট একটি চারা।
“ওইটা লাগিয়েছিল রায়হান মারা যাওয়ার পরদিন,” — কুন্তলা বলল পেছন থেকে। “তখন ও একটাও কথা বলেনি। শুধু গাছটা পুঁতে বসে ছিল।”
অভিক ক্যামেরা নামিয়ে ফেলল। তার চোখে জল।
ধুলেশ্বরীর আকাশে তখন সন্ধ্যার মেঘ জমছে, কিন্তু সেই মেঘে ভয় নেই।
সেই মেঘ এখন নতুন জলের প্রতিশ্রুতি।
গ্রামটা এখনও অনেক দুঃখে ভরা, অনেক সমস্যায় ডুবে আছে—কিন্তু একটা চিহ্ন তৈরি হয়েছে।
একটা রেখা, যা কাদার ভেতর থেকেও উঠে আসছে সবুজ হয়ে।
আর সেই সবুজের মাঝেই লেখা আছে একটা কথা:
“আমরা হারিনি। এখনো বাঁচছি।”
নোনা জলের রাজনীতি
ধুলেশ্বরীর ওপর বসন্ত তখন ধীরে ধীরে ছায়া ফেলছে।
বিকেলে পুকুরের ধার ঘেঁষে ছেলেমেয়েরা খেলছে, আর নারীরা জল টেনে গাছকে দিচ্ছে।
জলপাঠশালার খুদে ছাত্ররা ছবিতে আঁকছে নদী, গাছ, আর বাড়ির উঠোনে জমে থাকা শালুকফুল।
এই শান্তির ভিতরে ঢুকে পড়ল একটা নীল-সাদা গাড়ি।
গায়ে লেখা:
“বঙ্গজল হাইড্রো প্রাইভেট লিমিটেড – পরিবেশ বান্ধব সৌর লবণ প্রকল্প”
দু’জন অফিসার নামল—একজন মোটা ফ্রেমের চশমা পরে, আরেকজন হাতে একটা মোবাইল ঘোরাতে ঘোরাতে হাঁটছে।
“কোনটা জহর মণ্ডলের বাড়ি?” — চশমাওয়ালা বলল।
গ্রামের মোড়ল, নিত্যানন্দ, সামনে এগিয়ে এল।
“আপনারা কারা? কী দরকার?”
চশমাওয়ালা পরিচয় দিল,
“আমি দীপক মজুমদার, প্রজেক্ট কনসালট্যান্ট। সরকার অনুমোদিত একটি ‘গ্রিন লবণ এক্সট্র্যাকশন’ প্রকল্পে আপনাদের বাঁধ ভাঙা জমি বরাদ্দ হয়েছে।”
“মানে?” — কুন্তলা চমকে উঠল।
“মানে হচ্ছে,” — মোবাইল-ঘোরানো লোকটি বলল —
“আপনাদের যেসব জমিতে চাষ হয় না, সেগুলোতে আমাদের কোম্পানি সৌর শক্তির মাধ্যমে সমুদ্রজল থেকে লবণ বানাবে। এতে কর্মসংস্থান হবে, রাজস্ব আসবে, আর সরকার পরিবেশ বান্ধব বলেই অনুমোদন দিয়েছে।”
গ্রামবাসীরা হতবাক।
“আপনাদের অনুমোদন কবে হল? আমরা তো কিছুই জানি না!” — সুজাতা চিৎকার করল।
“মন্তব্য জমা দেওয়ার সময় দেওয়া হয়েছিল পঞ্চায়েতে, কারও কোনো আপত্তি আসেনি,” — দীপক বলল ঠান্ডা গলায়।
“আমরা তো কোনোদিন শুনিইনি!” — জহর বলল রাগতভাবে।
“আপনারা তখন ঘূর্ণিঝড় সামলাচ্ছিলেন। সে সময় সরকারি বিজ্ঞপ্তি কেউ পড়ে না—এটা কি আমাদের দোষ?” — মোবাইল-ঘোরানো লোকটি কটাক্ষ করল।
তিন দিন পর ব্লক অফিস থেকে এসেছিল আরও কিছু লোক—প্যাড হাতে, মানচিত্রে আঁকা জমির খতিয়ান।
তারা জানিয়ে গেল, ‘অবচাষযোগ্য’ জমির উপর আগামী তিন মাসের মধ্যেই প্রকল্প শুরু হবে।
“এই জমিতে তো আমরা চারা লাগিয়েছি, বৃক্ষরোপণ করেছি!” — কুন্তলা বলল।
“তাতে কী? সরকারি নথিতে জমি ‘চাষযোগ্য নয়’ বলেই তালিকাভুক্ত। আপনাদের ব্যক্তিগত আবেগ দিয়ে আইন পাল্টানো যায় না,” — অফিসার জবাব দিল।
রাতের বেলা জহর ডাকল সব গ্রামবাসীকে।
স্কুলঘরের নিচে আলো জ্বেলে বসে সবাই।
“আমরা এবার একজোট না হলে সবকিছু হারাবো,” — জহর বলল।
“কিন্তু কীভাবে? ওরা তো সরকারপক্ষ!” — কেউ একজন বলল।
“আমরা যদি ‘কমিউনিটি বন রক্ষা ও জল সংরক্ষণ কমিটি’ তৈরি করি, তাহলে জমির ওপর আইনি দাবি করা সম্ভব হবে। আর যদি ভিডিও, রিপোর্ট, ডেটা থাকে—যেটা রীমাদি আর অভিক তুলেছে—তাহলে আমরা জনমত তৈরি করতে পারি,” — সুজাতা বলল।
পরদিন ভোরে, অভিক ফোনে ভিডিও আপলোড করল ইউটিউব চ্যানেলে:
“ধুলেশ্বরীর সবুজ বিপ্লব বনাম নোনা জলের দখল”
শিরোনামে ছিল:
“একটা গ্রামের জীবন বনাম একটা কোম্পানির লাভ: কী বেছে নেবে বাংলা?”
ভিডিওতে দেখা গেল কুন্তলার ছেলে গাছের পাশে দাঁড়িয়ে বলছে,
“এই গাছটা আমার ভাইয়ের নামে। এটা কাটতে দেব না।”
এক সপ্তাহ পর, কলকাতার একটি সংবাদমাধ্যম রিপোর্ট করল:
“সৌর লবণ প্রকল্পে গ্রিনলিস্টেড জমিতে গ্রামবাসীদের চাষ চলছে — সরকার নিশ্চুপ”
সেই রাতেই একজন স্থানীয় নেতা এসে দেখা করলেন জহরের সাথে।
“দ্যাখো, আমি বুঝি তোর আবেগ। কিন্তু একটু সমঝোতা করে নে। কোম্পানি বলেছে ২৫ জনকে কাজ দেবে, তুই আগে নাম পাঠা।”
জহর চুপচাপ শুনছিল। শেষে বলল,
“আমরা কোনো ‘চাকরি’ চাই না যার বিনিময়ে গাছ কেটে নদী আবার বাঁধ ভাঙবে। আপনারা চাইলে আমাদের সাথে থাকুন, না হলে সামনে দাঁড়াবেন না।”
সেই রাতে কারা যেন এসে সদ্য পোঁতা দুটি গাছ কেটে দিল।
পুকুরের পাড়ে পড়ে রইল ভাঙা চারাগুলো।
কুন্তলা দাঁড়িয়ে দেখে বলল,
“ওরা ভয় দেখাচ্ছে।”
“ভয় দেখালে ভয় পেতে হবে—এই কথাটা সত্যি নয়। আমরা ভাঙব না,” — জহর বলল।
একদিন সকালে রীমা ফের এলেন, হঠাৎ করেই।
“আমি দিল্লিতে রিপোর্ট জমা দিয়ে ফিরে এলাম। পরিবেশ মন্ত্রণালয় ধুলেশ্বরীর গল্প শুনেছে। এখন তোমাদের লড়াই আমরা রাষ্ট্রীয় পরিবেশ আদালতে তুলব।”
“তবে মনে রেখো,” — তিনি বললেন,
“লড়াই এখন শুরু হয়েছে, শেষ হয়নি।”
নদী তখন আবার শান্ত, কিন্তু তার বুকের নিচে যেন টান পড়ে গেছে।
কখন যেন আবার এক ঢেউ উঠবে—সে ঢেউ লবণেরও হতে পারে, বিপ্লবেরও।
আর গ্রামবাসীরা, যারা একদিন কাদায় ডুবে ছিল, তারা এখন শিখে গেছে দাঁড়াতে।
জলকে চিনেছে, জমিকে ভালোবেসেছে, আর রাজনীতিকে মুখোমুখি হতে শিখেছে।
জলেই প্রতিকার
নোনা জলের প্রকল্প যখন ঘনিয়ে আসছে, তখনই ধুলেশ্বরীর মানুষ আর এক দিক খুঁজে পেল—জলকে প্রতিরোধ না করে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা।
জহর একদিন বলল,
“আমরা যদি জল আসার রাস্তা বন্ধ না করতে পারি, তবে সেই জল যেন জমা না থেকে কাজের আসে—এইটা ভাবতে হবে।”
সুজাতা তখন তুলে আনল একটা পুরনো কথা—তার বাবার আমলের।
“আগে আমাদের গ্রামে ‘চুঙি’ বসানো হতো—বাঁশ আর কাদা দিয়ে বানানো একধরনের জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা। বৃষ্টির সময় সেই চুঙি দিয়ে বাড়তি জল পুকুরে গিয়ে পড়ত। এখন সব বন্ধ।”
“তা হলে কেন আবার শুরু করা যাবে না?” — শুভদীপ বলল।
পরের দিন থেকে শুরু হল পরীক্ষা। বাঁশ, খড় আর কাদা দিয়ে বানানো হল ছোট ছোট বাঁধ।
এই বাঁধে ফুটো করে বসানো হল কাঠের নল। জল জমলে সে নল দিয়ে ধীরে ধীরে পাশের খালে চলে যাবে।
রীমা এই প্রক্রিয়ার ভিডিও তুলে পাঠাল এক পরিবেশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে।
তারা জানাল,
“আপনারা যা করছেন, সেটাই হলো স্থানীয় অভিযোজন। বিদেশেও এই প্রযুক্তির নাম ‘Slow Release Buffering Drainage’।”
এদিকে পুকুরটা যেটা কাদায় পরিণত হয়েছিল, তাকে ঘিরে শুরু হল ‘ভেট কেয়ার’ প্রকল্প।
মাটির নীচে নল বসিয়ে কয়েক ফুট গভীরে থাকা মিঠে জলকে তুলে এনে সেই পুকুরে ঢোকানো শুরু হল।
এই জলের উৎস ছিল পঞ্চায়েত অফিসের পাশে পুরনো টিউবওয়েল—যেটা এখন আর কেউ ব্যবহার করত না।
“আমরা পুকুরকে শুধুই জলাধার হিসেবে দেখছি না। এটা হবে মাছ চাষ, জলপথ ও বৃষ্টিজলের পুনর্ব্যবহারের কেন্দ্র,” — সুজাতা বলল।
অভিক, যাকে আগেও অনেকে শুধুই “ফোটোগ্রাফার” ভাবত, এবার সোলার পাম্প বানানো শুরু করল।
পুরনো পাখার অংশ, মোটরের কিছু যন্ত্রাংশ আর সোলার প্যানেল নিয়ে সে বানাল একটি জলতোলার ব্যবস্থা, যা দিনে ৩ ঘণ্টা করে জল তুলবে।
“এইটা পুকুর থেকে গাছের গোড়ায় জল পৌঁছে দেবে,” — সে বলল।
সকলের চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল।
“তুই তো পাগল! কিন্তু ভালোর জন্য পাগল,” — হাসতে হাসতে বলল কুন্তলা।
এবার বাচ্চাদের নিয়ে শুরু হল এক অভিনব খেলা—‘জলযোদ্ধা’।
স্কুলঘরের মাঠে পাঁচটি দল। সবাইকে দেওয়া হয়েছে একেকটা কাগজের মানচিত্র।
কোথা জমে জল, কোথায় বেশি গাছ, কোথায় প্লাস্টিক পড়ে—এইসব শনাক্ত করতে তারা ছুটে বেড়ায়।
এক বাচ্চা চেঁচিয়ে উঠল, “এখানে ড্রেন বন্ধ হয়ে আছে! জল বেরোতে পারছে না!”
“তাহলে করো না বন্ধ—তুমি তো জলযোদ্ধা!” — সুজাতা বলল হাসতে হাসতে।
বছর ঘুরে আবার এল বর্ষা।
আকাশে মেঘ, বাতাসে হিম।
কিন্তু এবার নদীর জল উপচে গ্রামে ঢুকছে না।
নতুন খাল, মাটির বাঁধ, চুঙি আর পুকুর—সব মিলিয়ে জল পাচ্ছে তার নিজের পথ।
প্রথমবার গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় জল দাঁড়ায়নি।
“এত বছর পর আমাদের উঠোন শুকনো থাকছে,” — কুন্তলার মা বললেন। “এইটা কি স্বপ্ন!”
এমন সময় এল এক চিঠি—পরিবেশ আদালত বঙ্গজল প্রজেক্ট স্থগিত করেছে।
চিঠিতে লেখা:
“স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোজন প্রচেষ্টা, সমাজভিত্তিক প্রকল্প ও ঐতিহ্যগত প্রযুক্তির প্রয়োগ বিবেচনায় এনে, উক্ত প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র স্থগিত করা হলো। নতুন পরিবেশ মূল্যায়নের আগে কোনো নির্মাণকাজ চলবে না।”
গ্রামের লোকজন সেই চিঠির কপি লেমিনেট করে স্কুলঘরে টাঙিয়ে দিল।
জহর দাঁড়িয়ে বলল,
“জল আমাদের শত্রু নয়। শুধু বুঝে নিতে হয় তাকে—কোথা দিয়ে আসবে, কোথায় যাবে, কতটা রাখব আর কতটা ছেড়ে দেব। সেই ভাষা একবার শিখে ফেললে, আমরা আর ডুববো না। সাঁতার কেটে চলতে শিখব।”
হাসিনা বলল,
“আমরা শুধু গাছ লাগাইনি। আমরা নিজেরা শিকড় ছড়িয়েছি এই মাটিতে। এবার কে আমাদের তুলবে?”
পিছনে বেজে উঠল একটা কণ্ঠ—
“নীল জলপথ তৈরি হচ্ছে ধুলেশ্বরীতে। এবং তার কারিগর সেই মানুষজন, যারা আগে ভেবেছিল—ওদের কিছুই বদলানো যাবে না।”
রীমা বলল হাসিমুখে,
“এটা এখন শুধু এক গ্রাম নয়। এটা এক পদ্ধতি। ‘ধুলেশ্বরী মডেল’—যেটা দেশজুড়ে অনুসরণ করা যাবে।”
ধুলেশ্বরী তখন ধীরে ধীরে আলোয় ভরছে।
পুকুরের ধারে নারকেলগাছ নড়ে উঠছে হাওয়ায়।
জলের ছায়ায় দেখা যাচ্ছে একটা নতুন ভবিষ্যৎ।
আর সেখানে লেখা—
“জলেই ভয় নয়, জলেই প্রতিকার।”
নীল ভবিষ্যতের খোঁজে
একটি বছর কেটে গেছে।
ধুলেশ্বরীর আকাশে এবার বসন্ত এসেছে অন্য রকম আলো নিয়ে।
সন্ধ্যায় পুকুরপাড়ের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকে ছোটরা, তাদের হাতে কাগজের ঘুড়ি, যার গায়ে বড় করে লেখা—
“জলই জীবন”।
রাতের অন্ধকারে মোড়ের চায়ের দোকানে ভিড়। মোবাইলের পর্দায় দেখা যাচ্ছে একটি লাইভ টেলিভিশন অনুষ্ঠান—“পরিবর্তনের ছায়ায় ভারত”।
সঞ্চালক বলছেন,
“আজ আমরা কথা বলছি ধুলেশ্বরীর মানুষদের সঙ্গে, যারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে জলবায়ু অভিযোজনের এক অভিনব মডেল তৈরি করেছেন। ধুলেশ্বরী এখন শুধু এক গ্রামের নাম নয়—এটা একটা পথ। ‘নীল জলপথ’।”
পর্দায় জহর, সুজাতা, কুন্তলা—সবাই। আর আছে বাচ্চারা, যারা তাদের গাছের নাম দিয়েছে মেঘলা, তৃষা আর প্রদীপ।
কলকাতার একটি পরিবেশ গবেষণা সংস্থা ধুলেশ্বরীকে বেছে নেয় একটি পাইলট প্রকল্পের জন্য—
“গ্রিন ফিউচার হ্যাব”।
এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য: স্থানীয় প্রযুক্তি, ঐতিহ্য ও আধুনিক অভিযোজনকে একত্র করে একটি নীল-সবুজ অর্থনীতি গড়া।
সুজাতা এখন মাসে দু’বার জল সংরক্ষণ নিয়ে অনলাইন ক্লাস নেয়, যেখানে উত্তরাখণ্ড, অসম, ওডিশা থেকে ছাত্রছাত্রীরা যোগ দেয়।
ধুলেশ্বরীর স্কুলঘর এখন শুধু পাঠশালা নয়—এটি এক গবেষণাগার।
রীমার দেওয়া নাম:
“জলপাঠ কেন্দ্র”।
এখানে শিশুদের শেখানো হয়—
কিভাবে বৃষ্টির জল ধরে রাখা যায়,
পুকুরের অক্সিজেন মাত্রা মাপার সহজ কৌশল,
কোন গাছ বেশি জল ধরে রাখে মাটিতে।
একদিন গ্রামে আসে কেন্দ্রীয় পরিবেশ দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি।
তাঁর বক্তব্য:
“ধুলেশ্বরীর মডেল এখন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রয়োগ করা হবে। একে বলা হচ্ছে—‘জলাভিযান-ধ’ মডেল।”
গ্রামের শিশু তৃষা তাকে প্রশ্ন করে,
“আপনারা অনেক আগে কেন আমাদের কথা শুনলেন না?”
প্রতিনিধি একটু থেমে বললেন,
“শহরের কাচের জানালায় মাটির গন্ধ ঢুকতে সময় লাগে মা। কিন্তু একবার ঢুকলে, সে আর যায় না।”
জহর আর কুন্তলা সিদ্ধান্ত নিলেন—ধুলেশ্বরী থেকে যেন কেউ না পালায়, আবার যেন বাইরে থেকেও কেউ আসতে পারে কিছু শিখতে।
তারা বানালেন “বৃক্ষবন্ধু অতিথিশালা”—যেখানে শহরের শিক্ষার্থীরা এসে থেকে শিখতে পারে,
আর স্থানীয় ছেলেমেয়েরা শিখতে পারে বাইরের জগতের সঙ্গে কথা বলা।
একদিন সন্ধ্যায়, অভিক তার ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে ওপরে উঠিয়ে ছবি তোলে।
ছবিতে দেখা যায়—গ্রামটা এখন যেন এক জল-গাছ-মানুষের জটিল কিন্তু সুন্দর নকশা।
পুকুরের চারপাশে গাছ, নতুন খালপথ, বৃষ্টির জল ধরে রাখা ছোট বাঁধ, সোলার প্যানেল আর তার পাশে খেলা করা শিশুদের ছোট ছোট ছায়া।
ছবিটার নাম রাখা হয়—“নীল ভবিষ্যতের নক্সা”।
পরদিন সকালে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় শিরোনাম:
“জলবায়ুর সঙ্গে যুদ্ধ নয়, সম্পর্ক—শেখাচ্ছে ধুলেশ্বরী”
আর নিচে ছোট করে লেখা:
“তখন সবাই ভেবেছিল এ গ্রাম ডুবে যাবে। এখন সবাই বলে, এ গ্রাম দেখিয়ে দিল কিভাবে ভেসে থাকতে হয়।”
বিকেলে যখন আবার নদীর ধারে বসে থাকে কুন্তলা, সে ভাবে—
একসময় এই জল ভয়ে কাঁপিয়েছিল তাদের। এখন এই জলই দিয়েছে ছায়া, শীতলতা, আশা।
পেছনে ছোট তৃষা বলল,
“তুমি বলেছিলে, নদীর বুকে খোলা থাকলে ভয় লাগে না। এখন বুঝি, নদীও কখনও কখনও মা হয়ে ওঠে।”
একদিন স্কুলে লেখা হল:
“আমরা জল ভালোবাসি। আমরা জলকে বোঝার চেষ্টা করি। আমরা জলকে শত্রু নয়, সাথী হিসেবে দেখি।”
রীমা বললেন,
“এই হল জলযোদ্ধার শপথ।”
শেষে, যখন সন্ধ্যায় ঘুঘু ডাকে আর ধানের গন্ধে বাতাস ভরে ওঠে, তখন নদীর জলে পড়ে এক লাল-হলুদ আলোর রেখা।
সেই রেখায় প্রতিফলিত হয় ধুলেশ্বরীর ভবিষ্যৎ।
এটি ‘নীল জলপথ’—একটি গ্রামের সাহস, প্রেম, ও জলবায়ুর সঙ্গে বোঝাপড়ার পথ।