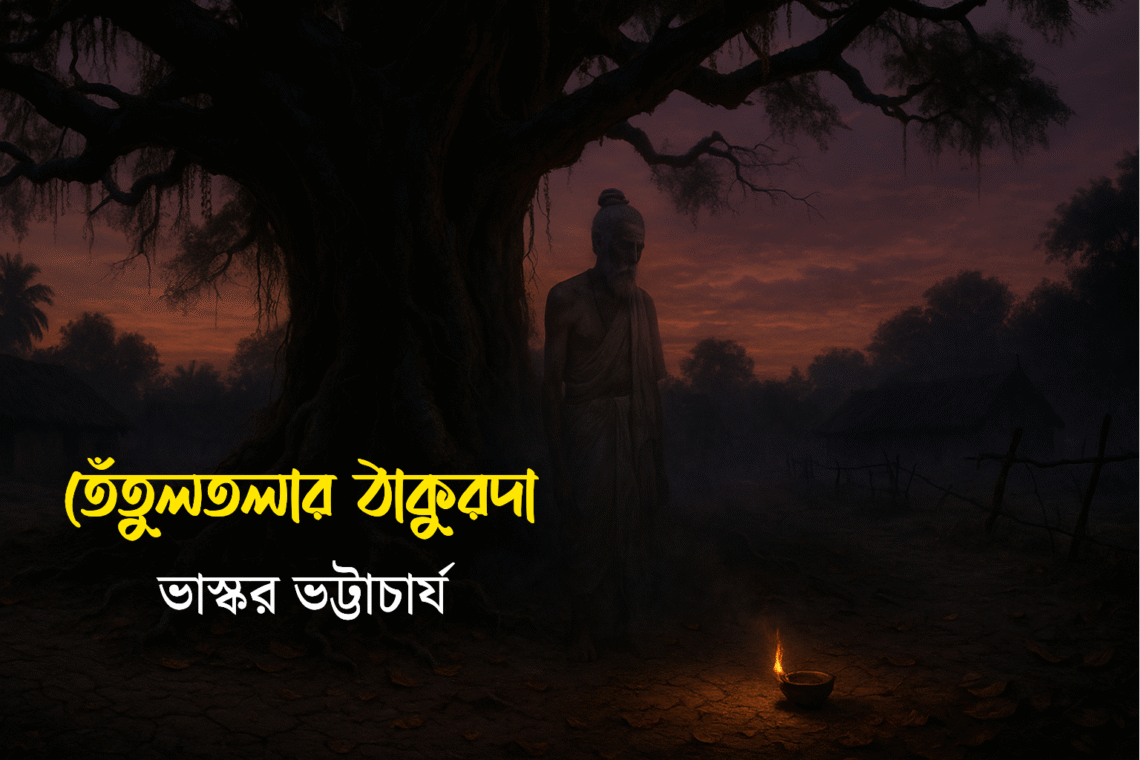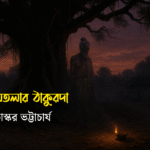ভাস্কর ভট্টাচার্য
১
নদিয়ার গ্রামের মেঠো রাস্তাগুলো যেন এখনো কুয়াশা গিলে রাখা স্মৃতির মতো। শহুরে ব্যস্ততার ভিড়ে পঁচিশ বছর পার করা অর্ঘ্য সেনগুপ্তর মনে হলো, গ্রামের মাঠের গন্ধটা আজও বদলায়নি। লাল মাটির পায়ে ধুলো লাগিয়ে সে নামল বাস থেকে, আর পেছনে তাকিয়ে দেখল একটুকরো ফেলে আসা সময় ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে। পেটচেরা রোদের মাঝে মাথার ওপর গাঢ় সবুজ তালগাছগুলো হেলে পড়েছে, পাশে পাটক্ষেতের গায়ে গায়ে গা ঘেঁষে সাঁই সাঁই করে ছুটছে দক্ষিণা বাতাস। স্টেশনের ধারে চায়ের দোকানে সেই পুরোনো হরিপদ কাকুর চায়ের হাঁড়ি এখনো উনুনে বসে, আর কাকুর চোখেমুখে সেই চেনা কৌতূহল—“চেনা চেনা লাগতেছে নাতি, তুই কি হরেন বাবুর ছেলেটা, অর্ঘ্য?” অর্ঘ্য হেসে মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ কাকু, আমি। বহুদিন পর এলাম।”
গ্রামটা বদলেছে অনেকখানি, তবে কিছু কিছু জিনিস রয়ে গেছে একেবারে আগের মতো। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমে এলে যখন অর্ঘ্য মাঠের ধারে হাঁটতে বেরোলো, তখন সে দেখল সেই বিশাল তেঁতুলগাছটা আজও দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের মাঝখানে, ঠিক আগের মতোই, ছায়া বিস্তার করে। গাছটা দেখতে যত না প্রাচীন, তার চেয়েও বেশি কিছু যেন আছে ওটার মধ্যে—একটা গম্ভীরতা, একটা নীরব শক্তি। হরিপদ কাকু পরে সন্ধ্যেবেলা চায়ের দোকানে বললেন, “ওই গাছের নিচে সন্ধ্যে হলে আর কেউ দাঁড়ায় না রে বাপ। বহু বছর আগে রামলোচন ব্রাহ্মণ—ওই ঠাকুরদা—ওইখানেই প্রাণত্যাগ করেছিলেন। তারপর থেকে জল্পনা। সন্ধ্যার পর কেউ গাছের পাশে গেলে তার গলায় নাকি ‘গলাটি’ জড়ায়। দড়ির মতো এক জিনিস, টান দিয়ে দম বন্ধ করে দেয়। গ্রামের ছেলেরা সাহস করে না, রে।” দোকানের সবাই গম্ভীর, শুধু অর্ঘ্য এক চুমুক চায়ে চুমুক দিয়ে হাসল, “গাছ কীভাবে দড়ি ছুঁড়ে ধরে মানুষ মারে বলুন তো?” সেই হাসির তলায় ছিল শহরের যুক্তিবাদ, গ্রামের রহস্যের ওপর তাচ্ছিল্য।
পরের দিন সকালবেলা অর্ঘ্য গেল মাঠের দিকে হাঁটতে, আর সেখানে দেখা হল মৌসুমির সঙ্গে—তার ছোটোবেলার খেলার সাথী। এখন সে গ্রামের স্কুলে পড়ায়, পরিপক্ক শান্ত মুখে একরকম অচেনা দুঃখের ছাপ। গাছটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে মৌসুমি ফিসফিস করে বলল, “তুই বিশ্বাস করিস না জানি, কিন্তু ওই গাছটা শুধু একটা গাছ নয় রে। ঠাকুরদা নাকি সেদিন এমন এক ব্রত নিয়েছিলেন, যেটা পূর্ণ না হলে আত্মাহুতি ছাড়া পথ ছিল না। সেই রাতেই উনি এই গাছের নিচে বসে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন। তারপর থেকে নাকি কেউ এলে গলাটি জড়িয়ে ধরে, যেন কেউ ওনাকে ব্যঙ্গ করলেই শাস্তি দেয়।” অর্ঘ্য আবার হেসে ফেলল, “তাহলে তো রোজ গবেষণা হতো ওখানে! শহরের লোক এসে হাড়গোড় নিয়ে যেত। অত কিছু হয় না। এসব লোককথা।” মৌসুমি আর কিছু বলল না, শুধু একবার তাকাল গাছটার দিকে। গাছটার ছায়া যেন তখন একটু বেশি দীর্ঘ, একটু বেশি ঘন।
২
“তুই শুধু ওই গাছটাকেই দেখিস, কিন্তু ওর চারপাশে যে কত কথা জড়ানো—তা জানিস না,” মৌসুমির গলার স্বরটা যেন সেই গাছের নিচের ছায়ার মতো গাঢ় আর বিষণ্ন। অর্ঘ্য তার কথা হালকাভাবে নিতে পারল না, কারণ মৌসুমি বলছিল খুব নিঃশব্দে, অথচ এমন এক তীক্ষ্ণ দৃঢ়তায়—যা অল্প বয়সে কোনো মানুষের থাকে না। তারা দুজনে তখন হাঁটছিল গ্রামের পুকুরের পাড় ধরে। পাশের শিউলি গাছের নিচে বসে মৌসুমি বলে চলল, “ঠাকুরদার নাম ছিল রামলোচন মুখোপাধ্যায়। গ্রামে তখন অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু উনি ছিলেন একেবারে আলাদা। গভীর তন্ত্রসাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন। অনেকেই বলত উনি মানুষ না, অর্ধেক দেবতা। এক সন্ধ্যায়, প্রায় পঁচিশ বছর আগে, হঠাৎ উনি গা ঢাকা দেন। তিনদিন পরে দেখা যায়, তেঁতুলগাছের নিচে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন—শরীর ঠান্ডা, নিঃশ্বাস নেই, কিন্তু চোখ খোলা। আর পাশে রাখা একখানা তালপাতার পুঁথি, যেটায় লেখা ছিল—‘এই আত্মা এখনও ত্যাগ হয়নি।’”
অর্ঘ্য কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। যুক্তি দিয়ে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু অনেক সময় কিছু অনুভূতির কোনো ছাঁকনি থাকে না। মৌসুমি আবার বলল, “সে রাতে একজন শিশু—পাঁচ বছরের একটি বাচ্চা ছেলে—গাছটার নিচে খেলে বেড়াচ্ছিল। তার মা বলত, বাচ্চাটা একসময় চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করে, আর বলেছিল, ‘ঠাকুরদা আমায় গলায় ধরছে! শ্বাস নিতে পারছি না।’ শিশুটি সেই রাতেই মারা যায়। তারপর থেকে সন্ধ্যার পর ওই গাছের ধারেকাছে কেউ যেত না। কেউ কিছু বলতে সাহসও করত না। শুধু শোনা যেত, রাতে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কার যেন দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে গাছের দিক থেকে, আর পাতাগুলো এক অদ্ভুত সুরে দুলতে থাকে—যেন মন্ত্রোচ্চারণ।” অর্ঘ্য মাথা নেড়ে হেসে বলল, “তুই তো দেখি গল্প লেখার মতো করে বলছিস! ভয় পাইয়ে দিচ্ছিস?” মৌসুমি সেই হাসিতে সাড়া দিল না, কেবল চোখ নামিয়ে বলল, “সব গল্প বানানো হয় না অর্ঘ্য, কিছু গল্প সময় বানায়, আর কিছু—ভয়।”
সেদিন রাতে ঘুম আসেনি অর্ঘ্যের। সে বারান্দায় বসে দূরে গাছটার দিকে তাকিয়ে ছিল। মাটির রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে সেই তেঁতুলগাছ যেন রাতের মধ্যে আরও লম্বা, আরও অন্ধকার মনে হচ্ছিল। হাওয়ার ঝাপটায় পাতাগুলো কর্কশ সুরে শব্দ করছিল—“ঝররর, ঝররর।” হরিপদ কাকু তখন চুপিচুপি এসে বসেন পাশে, হাতে কাপে চা। অর্ঘ্য বলে, “তেঁতুলগাছটা নিয়ে এত ভয় কেন, কাকু?” হরিপদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, “ভয় নয় বাবা, সেটা একরকম শ্রদ্ধা। ঠাকুরদা রামলোচন শুধু সাধক ছিলেন না, তিনি শেষ বয়সে বলতেন—‘যে জ্ঞান আত্মহীন, সে তমসিক।’ তিনি চাইতেন ও গাছের তলায় তাঁর আত্মার শক্তি থাকুক, যাতে মানুষ মনে রাখে, কিছু শক্তি যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না।” অর্ঘ্য বুঝতে পারছিল, সে একটা এমন কিছু ছুঁতে শুরু করেছে যার শিকড় কেবল বিশ্বাসে নয়, আত্মার ভিতরে। রাত বাড়ে। গাছের গায়ে তখন আর পাতার নয়, ছায়ার সরে যাওয়ার শব্দ, যেন কেউ ধীরে ধীরে নামছে—তাঁর মতো করে, নিঃশব্দে।
৩
সকালবেলা উঠেই অর্ঘ্য হাঁটতে বেরোল। দিনের আলোয় তেঁতুলগাছটাকে দেখে তার হাসি পেল—গাছটা যেন আর পাঁচটা গাছের মতোই। মোটা কাণ্ড, গায়ে মেছো সবুজ শৈবাল, মাটির দিকে ঝুঁকে থাকা একগুচ্ছ শিকড়। কিন্তু ওই গাছকে কেন্দ্র করেই গোটা গ্রামের এত ভীতি! সে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে চায়ের দোকানের দিকে তাকাল, যেখানে কিছু লোক ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছে। মৌসুমি তখনই এল, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যাবার পথে। “তুই কাল রাতে ঘুমাসনি তো?” —জিজ্ঞেস করল সে। অর্ঘ্য হেসে বলল, “ভয় পেয়ে ঘুমাতে পারিনি রে। তবে ভাবছি, ভয়টাকে একটু চেখে দেখা যাক।” মৌসুমি থমকে গেল। “মানে?” অর্ঘ্যের চোখে তখন এক চেনা বিদ্রুপের ঝিলিক—“আমি আজ রাতে তেঁতুলগাছের নিচে বসে থাকব। একা। দেখি, গলাটি আসে কিনা।”
বিকেলের দিকে খবরটা চায়ের দোকান হয়ে গ্রামের গলিপথে ছড়িয়ে পড়ে। “কলকাতার ছেলেটা নাকি রাতে তেঁতুলতলায় থাকবে!”—মাটির পাত্রে চায়ের চুমুকের সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ঘুরতে থাকে। অনেকে ভয় পায়, অনেকে কৌতূহলী হয়, কেউ কেউ হেসে বলে—”এ তো মরেই যাবে!” কিন্তু হরিপদ কাকুর মুখ গম্ভীর। সন্ধ্যার আগে তিনি নিজে এসে অর্ঘ্যর ঘরের বারান্দায় বসেন, আর বলেন, “শোন, আমি জানি তুই সাহসী, তোর যুক্তির হাত শক্ত। কিন্তু সব জিনিস যুক্তির বাইরে, কিছু অনুভূতির ব্যাখ্যা হয় না। আমি নিজে অনেক রাত ডিউটির পরে ওই গাছের পাশ দিয়ে এসেছি। কী যে হাওয়া আসে, কী যে ছায়া পড়ে, বুঝতে পারিস না। যদি কিছু হয়?” অর্ঘ্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেসে বলে, “কিছুই হবে না কাকু। আমি শুধু প্রমাণ করতে চাই—এই ভয়টা এক পুরনো কুসংস্কার। আমার গলায় কিছু আসবে না।”
সন্ধ্যে নামতে নামতেই গ্রামের মাঝখানে ছোট্ট এক আলোড়ন। হ্যারিকেন জ্বেলে অর্ঘ্য বসে পড়ে গাছটার নিচে। হাতে একটা নোটবুক, আর পাশে বোতলভরা জল। গ্রামের লোক দূর থেকে তাকিয়ে থাকে। কেউ কাছে আসে না, শুধু মৌসুমি দূরে দাঁড়িয়ে বলে, “তুই ফিরে আসবি তো, অর্ঘ্য?” অর্ঘ্য চোখ টিপে বলল, “আমার নামে গলাটি যদি আসে, তবে আগে সে যুক্তিকে ছুঁয়ে দেখুক।” ঘড়ির কাঁটা নড়ে এগিয়ে যায় রাত দশটার দিকে। চারপাশ নীরব। কেবল পাতার শব্দ—ঝররর… ঝররর… হঠাৎ কোথা থেকে এক ঠান্ডা বাতাস উঠে আসে, হ্যারিকেনের আলো কেঁপে ওঠে। অর্ঘ্যর মনে হল, শিকড়ের নিচে কোথাও যেন মাটি নড়ছে। দূর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ আসে—না, মানুষের না, কিন্তু বড্ড মানবিক! সে এক মুহূর্তের জন্য কলমটা ফেলে দেয়। বুকের ভেতরটা টান টান হয়ে যায়। কে যেন ধীরে ধীরে… এগিয়ে আসছে।
৪
রাত ঠিক দশটা বাজে। চুপচাপ গাছের নিচে বসে অর্ঘ্য। চারপাশে নিঃস্তব্ধতা এমন, যেন বাতাসেরও হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে গেছে। তার পাশে রাখা হ্যারিকেনের আলো এখনো জ্বলছে, কিন্তু সে বুঝতে পারছে—আলোটা আর তেমন সান্ত্বনা দিচ্ছে না। পাতা ঝরছে না, অথচ পাতার গায়ে অদ্ভুত শব্দ। যেন কেউ খুব ধীরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। দূর থেকে কুকুরের ডাকে একবার আওয়াজ হয়, তারপর আবার নিস্তব্ধতা। অর্ঘ্যর ঘাম ছুটে গেছে, যদিও সে এখনো নিজেকে জোরে ধরে রেখেছে। গাছের দিকে তাকিয়ে সে নিজেই হাসার চেষ্টা করল, “তুই যদি থাকিসও, ঠাকুরদা, আমি ভয় পাই না। কারণ আমি যুক্তিতে বিশ্বাস করি।” কিন্তু সেই বিশ্বাসটা একাই বসে থাকতে থাকতে, ধীরে ধীরে শরীরের কোথাও যেন খসে পড়ছে।
আচমকা ঠান্ডা একটা বাতাস এসে তার গায়ের ওপর দিয়ে ছুটে গেল। সে চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল—একটা পাতাও নড়ছে না, কিন্তু শীতের রাতের মতোই কাঁধে ঠান্ডা জমে যাচ্ছে। হ্যারিকেনের শিখা একবার কাঁপল, তারপর এক মুহূর্তের জন্য নিভে গেল। চারদিক ঘন অন্ধকার। অর্ঘ্য দমবন্ধ করে বসে আছে। তার পেছনে কে যেন ধীরে ধীরে হাঁটছে—মাটিতে শিকড় আর পাতা চাপা পড়ে এক অদ্ভুত শব্দ তুলছে, চট্ চট্… চট্ চট্…। তার গলার কাছে হঠাৎই ঠান্ডা কিছু স্পর্শ করল—না, জল নয়, বাতাস নয়—একটা ভারী, বরফঠান্ডা অস্তিত্ব। যেন কাপড় বা দড়ির মতো। সেটা আস্তে আস্তে তার গলায় পাক খেতে শুরু করল। অর্ঘ্য হঠাৎ অনুভব করল—সে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। “কে… কে?” তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। সেই ঠান্ডা জিনিসটা তার গলায় এমনভাবে চেপে বসেছে, যেন একশো বছরের রাগ জমে আছে।
কোনও মুখ নেই, কোনও চোখ নেই—কিন্তু সে বুঝতে পারছে, কেউ তাকিয়ে আছে। গাছের গায়ে যেন আলোছায়ার খেলায় ভেসে উঠছে এক পুরুষাকৃতি মুখ, চোখ দুটো গভীর আর জ্বলন্ত। তার ভিতরে কাঁপুনি উঠে যায়। মুখটা বলে, “বিশ্বাস করিস না? তুই তুচ্ছ করেছিস আত্মত্যাগ, ভেবেছিস আমি নেই?” সে আওয়াজ করে না, কথা আসে সরাসরি মাথার ভেতরে, যেন এক পুরনো পুঁথি থেকে উচ্চারিত হচ্ছে মন্ত্র। অর্ঘ্যর চোখ জলে ভরে আসে। সে দম নিতে পারছে না, তার মনে হচ্ছে, শরীরটা পাতার মত হালকা হয়ে গিয়েছে। আরেকটু হলে সে অচেতন হয়ে পড়ত, ঠিক সেই মুহূর্তে দূরে হ্যারিকেন আবার জ্বলে উঠল, আর সেই মুখটা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। গলার ওপরের শীতল অনুভবটা ফুস করে মিলিয়ে গেল বাতাসে। অর্ঘ্য গাছের গায়ে হেলে পড়ে নিঃশ্বাস নিতে থাকল, বুক ফুলিয়ে হাওয়ার খোঁজ করল, যেন সে সমুদ্রের নিচ থেকে ভেসে উঠেছে। চারদিকে তখনও কেউ নেই, শুধু দূরে কোথাও পেঁচা ডাকছে।
৫
ভোররাতের শেষপ্রান্তে পাখির ডাক উঠতেই গ্রামের কয়েকজন সাহস করে তেঁতুলগাছের দিকে এগোয়। তাদের হাতে লাঠি, চোখে ভয় আর কৌতূহলের ছায়া। তারা গাছতলার দিকে যেতেই দেখে—অর্ঘ্য মাটিতে পড়ে আছে, চোখ বন্ধ, মুখ জলে ভেজা, আর গলায় একটি অদ্ভুত লালচে দাগ। দড়ির মতো ঘূর্ণি পাকানো সেই দাগ দেখে একজন চিৎকার করে ওঠে, “ওরে, সত্যিই গলাটি ওকে ধরেছিল!” মুহূর্তে চারপাশে শোরগোল। মৌসুমি দৌড়ে আসে, হাঁটু গেড়ে বসে অর্ঘ্যর মাথাটা কোলে নেয়। ঠোঁট কাঁপে, মুখে ফিসফিস করে—“তুই কিছু করিসনি, অর্ঘ্য… ওকে ব্যঙ্গ করিসনি… তবু কেন এল?” অর্ঘ্যর চোখ তখনো বন্ধ, কিন্তু তার শরীর ধীরে ধীরে নড়ছে, যেন ঘুম ভাঙছে।
চোখ খুলতেই অর্ঘ্য প্রথম যেটা অনুভব করল তা হল বুকের ভিতরে এক চাপা জ্বালা আর গলার চারপাশে দগদগে ব্যথা। সে অস্পষ্টভাবে ফিসফিস করল, “সে… এসেছিল। গলায়… দড়ি…” চারপাশের মুখগুলো অস্পষ্ট, শুধু মৌসুমির মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—চোখে জল, ঠোঁটে প্রার্থনার মতো নীরবতা। তাকে গ্রামের প্রাথমিক চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হয়। পরানজীবা ঠাকুমা, যিনি ওই কাহিনির জীবিত সাক্ষী, এসে বসেন তার পাশে। অর্ঘ্যর হাতটা ধরে তিনি খুব ধীরে বলেন, “তুই ওকে ডাকিসনি, কিন্তু ও আসে তখনই—যখন কেউ ‘না’ বলে, অবিশ্বাস করে, অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। ও গলাটি নয় রে বাবা, ও আসলে তার আত্মার প্রমাণ। রামলোচন ব্রাহ্মণ নিজের গলাতেই দড়ি বেঁধে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন এক ব্রতের শেষ লগ্নে। সেই দড়ির শক্তিই আজ ‘গলাটি’ হয়ে ফিরে আসে।”
অর্ঘ্য কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে, “কিন্তু কেন আমায় ছেড়ে দিল?” ঠাকুমা একটু হেসে বলেন, “কারণ শেষ মুহূর্তে তুই ভয় পেয়েছিলি, বিশ্বাস করেছিলি যে সে আছে। তুই তোর অহং ছেড়েছিস, সেই ভয়ই রক্ষা করেছে তোকে।” এই কথাগুলো যেন অর্ঘ্যের ভিতরের জগতে এক আলো জ্বালায়। সে হঠাৎ বুঝতে পারে, গাছটা কেবল একটি অভিশপ্ত জায়গা নয়—তা এক শক্তির কেন্দ্র, যেখানে আত্মা, অহংকার ও বিশ্বাস একসঙ্গে বাস করে। সে বলে, “আমি… আমি যদি ওর কথা লিখি? ওর গল্পটা সবাইকে জানাই?” ঠাকুমা বলেন, “লিখিস, কিন্তু শুধু ভয় নয়—ভেতরের সত্যিটাও লিখিস। ভয় তো বাহানা, আসল কথা হল—মানুষ বিশ্বাস না করলে আত্মাও ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়।”
৬
পরের দিন দুপুর। অর্ঘ্য এখনও পুরোপুরি সুস্থ নয়, কিন্তু শরীরের ক্লান্তির তুলনায় তার মনের তৃষ্ণা অনেক বড়। সে জানতে চায়—কে ছিলেন সেই রামলোচন ব্রাহ্মণ? কেনই বা তার আত্মা এত বছর পরও গাছটায় বাস করছে? সেই প্রশ্নের জবাব একমাত্র জানেন পরানজীবা ঠাকুমা। অর্ঘ্যকে সামনে বসিয়ে তিনি ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন—“শুন, আমি তখন নববধূ। এই গ্রামে সদ্য এসেছি। রামলোচন ব্রাহ্মণ ছিলেন আমাদের ঘরের পাশের বাড়ির পুরোহিত—কিন্তু তিনি কেবল যজ্ঞ বা পূজায় সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন ‘উচ্চতর ব্রতচারী’, যার উদ্দেশ্য ছিল আত্মশুদ্ধি। তিনি বলতেন—‘মানবজীবন কেবল জন্ম আর মৃত্যু নয়, তা হল ত্যাগ আর উপলব্ধির সেতুবন্ধ।’ তিনি একদিন বললেন, তিনি ‘উগ্রসাধন’ নামের এক গোপন ব্রত নিতে চলেছেন—যার শেষ পর্যায়ে তাঁকে ‘আত্মত্যাগ’ করতে হবে… স্বেচ্ছায়, শান্তভাবে।”
অর্ঘ্যের চোখ বিস্ফারিত। ঠাকুমা বললেন, “গ্রামে কেউ এই কথা বিশ্বাস করতে চায়নি। সকলে ভাবত, তিনি পাগল হয়ে গেছেন। কিন্তু আমি জানতাম—তাঁর চোখে ছিল এক অন্য জ্যোতি। তেঁতুলগাছটা ছিল তার ‘আত্মস্থানের’ জায়গা। তিনি বলতেন—‘এই গাছের ছায়াতেই আমি নিজেকে অন্ধকারে সঁপে দেব, যাতে আলো আর ছায়ার দ্বন্দ্ব থেকে উঠে আসে পরিত্রাণ।’ যে রাতে তিনি আত্মাহুতি দেন, আমি জানি—কারণ আমি সেই রাতেই গোপনে দেখে ফেলেছিলাম শেষ দৃশ্যটা। গলায় একটি পাঁজরের তৈরি মালা পরা, চোখে তিলক, আর ঠোঁটে স্তব। তিনি দড়ি বাঁধছিলেন নিজের গলায়। আমি চিৎকার করব ভাবছিলাম, কিন্তু কিছু বলার আগেই এক অদ্ভুত আলোয় গাছের ছায়া নেমে এল তাঁর ওপর, আর তিনি নিঃশব্দে ঝুলে পড়লেন। না, ভয় পাইনি, কাঁদিনি—কারণ সে দৃশ্য ছিল ভয় নয়, এক চূড়ান্ত শান্তির।”
অর্ঘ্য চুপ করে শুনছিল। ঠাকুমার কণ্ঠ তখন একটানা কাঁপছে না, বরং একধরনের গর্বে ভরা। “তারপর থেকেই, আমরা বুঝলাম, ঠাকুরদা সেই গাছেই রয়ে গেছেন। শুধু নয়নে নয়, অনুভবে। তাঁর আত্মা কেবল ভয় ছড়ায় না, সে চায় শ্রদ্ধা। কেউ অবিশ্বাস করলে, সে ফিরে আসে, কারণ তার আত্মত্যাগ যেন ব্যর্থ না হয়। ‘গলাটি’ মানে দড়ির ছায়া নয়, তা হল স্মৃতির টান, যা অন্ধকার থেকে আলোকে ডাক দেয়।” অর্ঘ্য চোখ নামিয়ে বলে, “আমরা তাকে ভূত বলেছি, ভয় দেখেছি, অথচ সে চেয়েছিল—তাকে কেউ মনে রাখুক… একজন মানুষ হিসেবে, এক সাধক হিসেবে।” ঠাকুমা হেসে বললেন, “তুই লিখে রাখিস এই কাহিনি, অর্ঘ্য। আজকের ছেলেরা ভয় এড়িয়ে চলে, অথচ ভয় নয়—শ্রদ্ধাটাই সবচেয়ে জরুরি। রামলোচন ব্রাহ্মণ কখনো মরে যাননি—তিনি রয়ে গেছেন এক ছায়ার মতো, এক শিক্ষার মতো।” গাছটার দিকে তাকিয়ে অর্ঘ্যর মনে হল—তার পাতাগুলো যেন আজ একটু বেশি নরম, একটু কম বিষণ্ন।
৭
তেঁতুলতলার সেই ভয়ঙ্কর রাত, গলায় জড়ানো সেই অদৃশ্য দড়ি, আর পরানজীবা ঠাকুমার মুখে শোনা ঠাকুরদার আত্মত্যাগের কাহিনি—সব মিলিয়ে অর্ঘ্যর ভেতরে যে আলোড়ন উঠেছে, তার গভীরতা সে নিজেও পুরোপুরি বোঝে না। সে হাঁটে, কথা বলে, চা খায়—কিন্তু তার চিন্তা স্থির থাকে একটি প্রশ্নে—“রামলোচন ব্রাহ্মণ কী চেয়েছিলেন?” গাছতলায় বসে সে চোখ বন্ধ করে বারবার সেই মুখটিকে মনে করতে চেষ্টা করে। ভয় আর গর্বে মেশানো এক মুখ, যা দুঃস্বপ্ন নয়, বরং বোধের দরজা খুলে দেয়। হঠাৎ একদিন সকালে সে মৌসুমিকে ডেকে বলে, “তুই বলেছিলি ঠাকুরদার কাহিনি কেউ লিখে রাখেনি, কেউ তাঁর ব্রতকে সম্মান দেয় না। যদি আমরা সেটা করি?” মৌসুমির চোখে কৌতূহল—“মানে?” অর্ঘ্য বলে, “একটা স্মরণ-অনুষ্ঠান, একটা লোকসংস্কৃতি উৎসব—তাঁর নামে। গ্রামের বাচ্চাদের নিয়ে একটি মঞ্চস্থ নাটক, যেখানে ঠাকুরদার ব্রতের কথা বলা হবে। ভয় না, শ্রদ্ধা দিয়ে মানুষ তাঁকে মনে রাখবে।”
প্রথমদিকে গ্রামবাসীরা দ্বিধায় পড়ে যায়। এত বছর ধরে ভয় আর কুসংস্কারের মধ্যে গড়ে ওঠা একটি ‘ভৌতিক গাছ’-এর চেহারা একেবারে পাল্টে দিতে চায় অর্ঘ্য? হরিপদ কাকু বলেন, “তুই সত্যিই ভাবছিস, গলাটির ভয় মুছে ফেলা যাবে?” অর্ঘ্য হাসে, “ভয় নয় কাকু, সত্যিটাই ছড়াতে চাই। ভয় তৈরি হয় অজানাকে ঘিরে—যদি জানি, যদি বুঝি, তবে ভয় থাকে না, শুধু শ্রদ্ধা থাকে।” ধীরে ধীরে মৌসুমির সাহায্যে সে শুরু করে এক নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখা—‘রামলোচনের ব্রত’। গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা অংশ নেয়, কেউ ঠাকুরদা, কেউ গ্রামের মানুষ, কেউ গাছ হয়ে দাঁড়ায়! rehearsals হয় সন্ধ্যার পরে, গাছের সামনেই, হ্যারিকেনের আলোয়। পরানজীবা ঠাকুমা নিজে কাহিনির পরামর্শ দেন, আর বলেন, “ও যখন ব্রত নিয়েছিল, তখন যেমন ভাবে বলত—‘এই ব্রত ত্যাগ নয়, এক নবজন্ম।’ ঠিক সেভাবে বলিস।”
অবশেষে উৎসবের দিন আসে। হরিপদ কাকুর তত্ত্বাবধানে তৈরি হয় ছোট্ট মঞ্চ, তেঁতুলগাছের সামনের খোলা জায়গায়। গাছের গায়ে এবার মালা, ধূপ আর প্রদীপ জ্বলে। সন্ধ্যে নামে, অথচ কেউ ভয় পায় না। আশেপাশের গ্রামের লোকও এসেছে। ছোট্ট ছেলেটি যখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলে, “আমি রামলোচন—আমার দেহ চলে যাবে, আত্মা থেকে যাবে তোমাদের মাঝে”—তখন গাছের পাতায় বাতাস বয়ে যায় এক অন্যরকম শব্দে। কেউ বলেনি কিছু, কিন্তু সকলেই বুঝেছে—তিনি এসেছেন, উপস্থিত হয়েছেন শ্রদ্ধায়, ভয় নয়। নাটক শেষে অর্ঘ্য গাছের সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে বলে, “আজ থেকে এ গাছ শুধু ভয় নয়, আমাদের ঐতিহ্যও। রামলোচনের ব্রত এক ত্যাগ, যা মানুষকে আলোর পথে টানে। তিনি আত্মা দিয়ে ছিলেন, আর আমরা আজ সেই আত্মাকে স্মরণে রেখে যেতে চাই।” মৌসুমি পাশে দাঁড়িয়ে, ঠাকুমা চোখের কোণে জল মুছছেন, আর গাছের পাতাগুলো যেন মাথা নোয়াচ্ছে, ধন্যবাদ জানাতে।
৮
এক বছর পেরিয়ে গেছে। নদিয়ার সেই ছোট্ট গ্রাম যেন বদলে গেছে চোখে পড়ার মতো। তেঁতুলগাছ আর “ভয়ের গাছ” নয়—এখন সে এক স্মৃতিচিহ্ন, এক পুরুষের আত্মত্যাগের নিদর্শন। প্রতি বছর আশ্বিন মাসের এক পূর্ণিমার রাতে “রামলোচন স্মরণ উৎসব” পালিত হয়। গ্রামের ছেলেমেয়েরা নাটক করে, গান গায়, স্থানীয় স্কুলে ঠাকুরদার ব্রতের উপর একটি পাঠ্যনাটকও পড়ানো হয় এখন। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে যে ছেলেটি ছিল—কলকাতা ফেরত যুক্তিবাদী অর্ঘ্য—সে আজ আবার এসেছে গ্রামের সেই পুরনো উঠোনে। কিন্তু এবার আর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে নয়, শ্রদ্ধা জানাতে।
সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামে। অর্ঘ্য এবার একা নয়, কিন্তু গাছের নিচে সে একাই বসতে চায়। গতবার সে যেখানে দম বন্ধ হয়ে পড়েছিল, আজ ঠিক সেখানেই সে বসে। সঙ্গে একটি ছোট্ট মাটির প্রদীপ, কিছু ধূপকাঠি, আর নিজের হাতে লেখা একটা চিঠি। চিঠির উপরে লেখা—“প্রিয় ঠাকুরদা”। বাতাস থমথমে, পাতাগুলোর শব্দ আসছে বটে, তবে সেই কর্কশ গুঞ্জন নেই। হ্যারিকেনের আলোয় সে চিঠিটা পড়ে শোনায়:
“তোমাকে ব্যঙ্গ করেছিলাম, ভয় পাইনি বলে গর্ব করেছিলাম। অথচ আজ জানি, তুমি শুধু আত্মা নও—তুমি স্মৃতি, তুমি ত্যাগ, তুমি আলো। তোমার সেই ‘গলাটি’—আমার গলায় নয়, মনে জড়িয়ে ছিল। আজ তোমায় স্মরণ করি শ্রদ্ধায়। বিশ্বাস করি, তুমি রয়ে গেছো আমাদের সঙ্গে।”
চিঠি পড়ে, সে ধূপ জ্বালায়। পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মৌসুমি, আর দূরে বসে রয়েছেন পরানজীবা ঠাকুমা, যিনি চোখ বন্ধ করে মন্ত্র আওড়াচ্ছেন। হঠাৎ বাতাস এক মুহূর্তের জন্য থেমে যায়, গাছের সব পাতা থেমে থাকে। অর্ঘ্য অনুভব করে—পেছনে দাঁড়িয়ে কেউ, কিন্তু এবার সেই উপস্থিতিতে ভয় নেই, আছে এক গভীর শান্তি। কেউ যেন কাঁধে হাত রাখল—নরম, হালকা, আশীর্বাদের মতো। চোখ বন্ধ করে অর্ঘ্য বলে, “আজ তুমি এসো, ভয় নয়—আলো হয়ে।” তখনই গাছের মাথার উপর হঠাৎ একঝলক পূর্ণিমার আলো ছায়া ফেলে, পাতাগুলো ধীরে ধীরে দুলতে শুরু করে। কিন্তু বাতাস বয় না, শব্দ নেই। এক অলৌকিক নিস্তব্ধতা ভর করে—যেখানে অর্ঘ্য বোঝে, “তিনি এসেছেন, এবার চুপচাপ বিদায় নিচ্ছেন”।
শেষরাতে অর্ঘ্য উঠে দাঁড়ায়, পেছনে তাকায় না। মৌসুমি কাছে এসে বলে, “কেমন লাগছে?”
অর্ঘ্য শুধু একটাই শব্দ বলে, “হালকা।”
সে জানে, তেঁতুলতলার ঠাকুরদা আজ আর “গলাটি” নন, তিনি এখন এক আশীর্বাদ—এক চিরজাগরুক উপস্থিতি।
সমাপ্ত