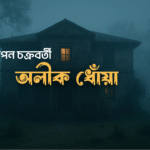দীপন চক্রবর্তী
পর্ব ১
ঘড়ির কাঁটা রাত সোয়া বারোটায় এসে থেমে গেছে যেন। কলকাতার উত্তরের এই পুরনো পাড়াটায় এমনিই রাতের নির্জনতা নেমে আসে একটু আগে, কিন্তু আজকের রাতটা যেন আরও ভারী, যেন বাতাসেও কেউ গোপনে নিঃশ্বাস ফেলছে। রায়চৌধুরি বাড়িটা ছিল এক সময় নামকরা জমিদারদের বাসভবন, এখন তা আধভাঙা প্রাসাদ, চারপাশে বড় বড় শালিকের ডাক আর পেছনের বাঁশবনে মৃদু শব্দে ফিসফিসে বাতাস।
আজ সেই বাড়ির একমাত্র উত্তরাধিকারী সায়ন্তন রায়চৌধুরি ফিরেছে বিদেশ থেকে, বারো বছর পর। এয়ারপোর্ট থেকে সে সোজা এসেছিল এখানেই, চালকের হাতে চাবি দিয়ে ঢুকেছিল সেই গম্বুজওয়ালা লোহার ফটক ঠেলে। কিন্তু তার ফেরা শুধুমাত্র একটা ছুটির কারণে নয়। পৈতৃক সম্পত্তির কাগজে স্বাক্ষর করতে হবে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি কিছু – একটা প্রশ্ন, যেটার উত্তর আজও মেলেনি।
সে তখন ক্লাস টুয়েলভে, তার বাবা আত্মহত্যা করেন এই বাড়ির ভিতরের লাইব্রেরির ঘরে। পুলিশের রিপোর্টে লেখা ছিল আত্মহত্যা, শ্বাসরোধ করে। কিন্তু সায়ন্তনের মনে হয়েছিল কিছু একটা ঠিক নেই। তার বাবার মুখের অভিব্যক্তি, যা শেষ বারের মতো দেখেছিল মর্গে, সেখানে যেন আতঙ্কের ছায়া লেগে ছিল—কোনও অপরাধীর নয়, বরং শিকারির মুখ।
বাড়ির পুরোনো পরিচারক হরিদাস এখনও রয়েছেন। এখনো সকালে চা বানান, সন্ধ্যায় আলো জ্বালেন। সায়ন্তন যখন ঢুকল, হরিদাস তার থরথর কাঁপা গলায় বলল, “আপনি তো আবার এলেন বাবু… এই বাড়িটা তো এখনো…”
“এখনো কী, হরিদাস?” সায়ন্তন জিজ্ঞেস করল।
হরিদাস তাকাল দোতলার দিকে, তারপর মাথা নিচু করে বলল, “রোজ রাতে কেউ হাঁটে বাবু… গলার আওয়াজ শোনা যায়… আগের মতোই।”
সায়ন্তন হাসল না, বিরক্তও হল না। সে বলল, “দেখি তো, এবার সত্যিটা ধরা যায় কিনা।”
রাত একটার সময় সে লাইব্রেরির ঘরের দরজা খুলল। ঘরটা একইরকম আছে—পুরোনো বুকশেলফ, চেয়ারটা উলটে পড়ে আছে ঠিক যেখানে বাবা পড়েছিলেন, আর জানালাটা হালকা ফাঁকা। সে একটা টর্চ জ্বালাল, খাটের পাশে একটা পুরোনো ডায়েরি পড়ে ছিল—তার বাবার হাতের লেখা। খোলা পাতায় লেখা ছিল—
“১৮ অক্টোবর, ২০১০। আমি জানি আজ রাতেই ও আসবে। আমি দরজা বন্ধ করে রাখব না। যদি এটা আমার শেষ দিন হয়, আমি জানি এটা লেখা থাকবে, কেউ পড়বে।”
সায়ন্তন শিউরে উঠল। তার বাবার মৃত্যুর আগের রাতের লেখা। তারিখটা মিলে যায়। এই লেখা তো কেউ জানত না, পুলিশ কেসেও এর উল্লেখ ছিল না। তাহলে এটা কে পড়েছে? কে জানত?
ঠিক তখনই, টর্চটা নিভে গেল। এবং ঘরের বাইরে থেকে একটা মৃদু পদচিহ্নের শব্দ ভেসে এল। একবার, দুইবার—ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। দরজার ফাঁক দিয়ে একটা ছায়া পড়ল মেঝেতে—একজন মানুষের ছায়া, কিন্তু মাথাটা যেন খুব অস্বাভাবিকভাবে বাঁকানো।
সায়ন্তন বুকের ভেতরে চাপা আওয়াজে বলল, “কে?”
কোনও উত্তর নেই। কেবল পদক্ষেপ।
সে সাহস করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, দরজাটা খুলে বাইরে তাকাল। করিডোরে কেউ নেই। কিন্তু দেয়ালে, ঠিক বাবার ছবিটার নিচে, লাল কালিতে একটা শব্দ লেখা ছিল—”আবার ফিরে এসেছ?”
সায়ন্তন হঠাৎ পিছিয়ে এল। এই লেখাটা নতুন। সে ছুঁয়ে দেখল—কালিটা এখনও ভিজে।
হঠাৎ তার মনে পড়ল—এই শব্দটা… হ্যাঁ, ঠিক এই শব্দটাই একবার শুনেছিল সে বাবার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাকালীন, সেই রাতে, অনেক আগের রাতে, যখন সে ফোনে কথা বলছিল, আর ভিতর থেকে বাবার গলা আসেনি—এসেছিল অন্য কারও।
তারপর আচমকা একটা ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে টর্চটা আবার জ্বলে উঠল। কিন্তু সে যখন পিছন ফিরল, তার বাবার চেয়ারটায় বসে কেউ একজন ছিল।
সায়ন্তনের মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোল না। কেবল তার বুকের ভেতরটা ঠেলে উঠে এল পুরোনো প্রশ্নটা—“সত্যিই আত্মহত্যা… নাকি কিছু আরেকটা?”
পর্ব ২
সায়ন্তনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। বাবার পুরোনো চেয়ারে যে লোকটি বসে আছে, তার মুখটা আধো আলোয় স্পষ্ট নয়, কিন্তু অবয়বটা যেন পরিচিত। মাথাটা একটু কাত করা, এক হাতে চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরা—অস্বাভাবিক নির্লিপ্ত ভঙ্গি। সায়ন্তনের গলা শুকিয়ে গেল, মুখে শব্দ আটকে গেল। হঠাৎ সে চোখ মুছে আবার তাকাল—কেউ নেই।
চেয়ার ফাঁকা। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল, হাত বাড়িয়ে চেয়ারে ছোঁয়াল। গায়ে হিম ঠান্ডা লেগে গেল। কিন্তু তাও নিজেকে স্থির রাখল। বুকের ভেতরে শব্দ করে কাঁপছে কিছু—ভয় নয়, আরও বেশি একটা অজানা কৌতূহল।
সে আলোটা ফের ঠিক করল, এবার চেয়ারের নিচে কিছু একটা দেখতে পেল—একটা চুলের ক্লিপ। একটা নারীর। চকচকে ধাতুর কাজ করা, পুরোনো দিনের স্টাইল। এই ঘরে একটা নারীর চুলের ক্লিপ কীভাবে এল?
সে হঠাৎ মনে করতে পারল না, তার বাবার মৃত্যুর রাতে কোনও নারী অতিথি ছিল কিনা। ডায়েরির পাতায় চোখ রাখতেই আরও একটা লাইন দেখা গেল—
“ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বোঝার চেষ্টা করেছিলাম ও মানুষ না কিছু আরেকটা।”
সায়ন্তনের শিরদাঁড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কে এই ‘ও’? আর কেন তার বাবা ভাবলেন সে মানুষ নয়?
হরিদাসকে ডাকতে গেল সে, কিন্তু দরজার কাছে যেতেই এক অদ্ভুত শব্দ কানে এল—পিয়ানোর সুর। খুব নরম, মৃদু, যেন দেওয়ালের ওপার থেকে বাজছে, আবার যেন কারও মনে। কিন্তু এই পিয়ানো তো… এই বাড়িতে তো কেউ বাজায় না, এবং বহু বছর ধরে বাজানোর মতো অবস্থাতেও নেই!
সে ছুটে নীচে গেল। বড় ড্রয়িংরুমে ধুলো জমে থাকা পিয়ানোর সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে হল কেউ হাত রেখেছে কীবোর্ডে। কেবলমাত্র দুটি সুর বারবার বাজছে, একই ছন্দে—মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে, যেন কেউ ভুল করছে।
সে ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে গেল। টর্চের আলোয় দেখতে পেল পিয়ানোর ওপরেও কিছু পড়ে আছে—একটা পুরোনো রুমাল, তাতে সূচিকর্ম করা নাম “S.K.”
সায়ন্তন থমকে গেল। এই নাম সে চেনে। স্মৃতির গহীনে খুঁড়ে সে মনে করতে পারল, তার বাবার ডায়েরির এক পেছনের পাতায় একবার সে এই আদ্যাক্ষর দেখেছিল—S.K. ওর চোখে নীল আলো ঝলসে ওঠে, আমি বুঝি ও ফিরে আসবে।
সে ডায়েরি নিয়ে আবার উপরে উঠল। নিজের ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রাখল সব ক্লু—চুলের ক্লিপ, রুমাল, ডায়েরি। হঠাৎ খেয়াল করল, ডায়েরির একটা পাতায় পেনের আঁচড় পড়ে গেছে, কিন্তু কিছু লেখা নেই—শুধু চাপা লেখার দাগ।
সে তার ফোনের আলো জ্বালিয়ে পাশ থেকে দেখল—হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চাপা লেখা—“ও আমাকে বলেছিল, সত্যি জানতে চাইলে বাগানের শেষ মাথায় গিয়ো। রাত তিনটের আগে।”
ঘড়ি দেখল সায়ন্তন—দুইটে পঁচিশ। তার মানে হাতে মাত্র ৩৫ মিনিট। সে ব্যাগ থেকে টর্চ নিয়ে নেমে এল নিচে, তারপর খোলা পেছনের দরজা দিয়ে বাগানের দিকে এগোল।
বাগান একসময় সাজানো ছিল—এখন কাঁটাঝোপ, গাছগাছালি আর জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। দূরের শেষ প্রান্তে একটা পুরোনো টিনের ঘর দেখা যায়, সেখানে এক সময় মালী থাকত। কিন্তু সেই ঘর বহু বছর ধরে বন্ধ।
সে কাঁটা ঠেলে, ঘাস পেরিয়ে টিনের ঘরের কাছে পৌঁছাল। হাত বাড়িয়ে দরজার হ্যান্ডেল ধরতেই সেটা সরে গেল তার হাতে—ভেঙে গেছে অনেকদিন। কিন্তু দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলল সে।
ভেতরে একটামাত্র কাঠের খাট, তার ওপর ধুলো পড়া একটা কুলুঙ্গি। আর কুলুঙ্গির ওপরে লেখা—“সত্য জানতে এসেছ?”
সায়ন্তন হঠাৎ পেছন ঘুরে তাকাল, কিন্তু কেউ নেই। আর তখনই টর্চ নিভে গেল। অন্ধকারে সে শুধু শুনল, হাওয়ার মতো একটা গলা ফিসফিস করে বলছে—“ও এখনো আছে, সায়ন্তন… তুমি ফিরে এসেছ বলেই ও জেগে উঠেছে।”
পর্ব ৩
সায়ন্তন থমকে দাঁড়াল। ফিসফিসে কণ্ঠস্বরটা যেন বাতাসের মধ্যেই গলে ছিল, কিন্তু ঠিক কানে এসে লাগল—জীবন্ত, গা ছমছমে। সে একটা চাপা শ্বাস নিয়ে আবার টর্চ চালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু আলো আর জ্বলল না। হাতে থাকা ফোনটাও কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। বুকের ভেতর ঘূর্ণি উঠছে, কিন্তু পেছন ফিরল না। বরং কুলুঙ্গির কাছে গিয়ে হাতে ছুঁয়ে দেখল সেই খোদাই করা লেখাটা—“সত্য জানতে এসেছ?”
লেখার নিচে কাঠের ফ্রেমে এক টুকরো পাতলা স্লেট বাঁধা ছিল, আর তার নিচে ঝুলে ছিল একটা লোহার চাবি। সায়ন্তনের মনেই হল—এই চাবিটাই যেন কোনও দরজার তালা খুলতে চায়, কোনও সত্যর গোপন দরজা। সে সেটা খুলে পকেটে রাখল।
ঠিক তখনই, খাটের নিচ থেকে একটা ঠক করে শব্দ হল। সায়ন্তন নিচু হয়ে দেখল—একটা কালো রঙের চামড়ার বাঁধানো ডায়েরি রাখা আছে। অনেকদিনের ধুলোমাখা, পৃষ্ঠাগুলো হলুদ। কিন্তু তার নামের প্রথম পাতায় লেখা—“সর্বাণী কুণ্ডু, ১৯৮৫।”
সায়ন্তনের ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল। S.K.—সর্বাণী কুণ্ডু? তাহলে এটাই সেই নারী? কিন্তু এই নাম তো তার পরিবারে কেউ কখনও বলেনি, কোনো নথিতে নেই, এমনকি তার মা-ও এ নামের কথা কখনো বলেননি।
সে ডায়েরির পাতা উল্টাতে থাকল—প্রথম দিকে ছোট ছোট কবিতা, কখনো বাংলায়, কখনো ইংরেজিতে। তারপর হঠাৎ একটা পাতায় বড় হরফে লেখা—“রায়চৌধুরি বাড়ির ইতিহাস লুকিয়ে আছে দরজার ওপারে, যেখানে সূর্য ঢোকে না।”
তারপর পাতাগুলোতে কিছু ছবি আঁকা—একটা বড় বাড়ি, নিচে তলা, অন্ধকার কুঠুরি। এবং তারপর একটা নীল কালির স্কেচে আঁকা একটা অদ্ভুত চিহ্ন—চক্রের মতো, মাঝখানে চোখের মতন একটা প্রতীক, যা সায়ন্তন আগে কখনো দেখেনি।
হঠাৎ তার মনে পড়ল লাইব্রেরির দেয়ালে একটা ক্যালিগ্রাফি টানানো ছিল অনেক আগে—সেই চিহ্নটা ওই ছবিতেও ছিল। ছোটবেলায় সেটা সে খেয়াল করেনি। এখন মনে হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে ওই চিহ্নটা জড়িয়ে আছে।
সে ডায়েরি হাতে নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে চলল। রাস্তা তখন একেবারে নিস্তব্ধ, আকাশে মেঘ জমে গেছে। বাড়িতে ফিরে লাইব্রেরিতে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে দেয়ালটা খুঁজতে শুরু করল—হ্যাঁ, এক কোণে পুরনো ধূলোমাখা ক্যালিগ্রাফিটা এখনও ঝুলছে। ধীরে ধীরে সেটা নামিয়ে তার পেছনটা ঘাঁটতে লাগল। হঠাৎ বোর্ডটা খানিকটা আলগা হয়ে খুলে গেল। আর ভেতরে সে যা দেখল, তাতে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।
একটা ছোট গোপন বক্স। ভিতরে রাখা একটা নীল কাচের পেন্ডেন্ট, এবং একটা পুরনো ফটো—সাদা-কালো, যেখানে তার বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক নারীর সঙ্গে, যার চুলে সেই একই ক্লিপ, এবং পরনে সাদা শাড়ি। তার বাবার মুখ হাসি হাসি, কিন্তু সেই নারীর চোখে সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকা এমন এক দৃষ্টি, যেন সে জানে ছবির ওপারেও কেউ আছে—দেখছে, জানছে, সন্দেহ করছে।
ছবির পেছনে লেখা ছিল, “আমার সর্বাণী—১৯৮৫, ল্যামার্ট স্কুলের পেছনের দিনগুলো।”
সায়ন্তন হঠাৎ বুঝতে পারল, এই নারী কেবল তার বাবার জীবনের অংশ নয়—পুরো রহস্যটার কেন্দ্রবিন্দু। এবং হয়তো এই মহিলাই সেই রাতে বাবার ঘরে এসেছিলেন। অথবা… হয়তো তিনি এখনও এই বাড়িতে আছেন—কোনও এক রূপে, কোনও এক অস্তিত্বে।
ঠিক তখনই একটা শব্দ হল—লাইব্রেরির দরজাটা হঠাৎ করে ভিজে কাঠের মতন খটাস করে বন্ধ হয়ে গেল। বাতাস নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল, আর একটা চেনা গলা শোনা গেল—“তুই ছবি দেখলি, কিন্তু গল্পটা এখনও জানিস না…”
সায়ন্তন গলা শুকনো স্বরে বলল, “কে? কে তুমি?”
আর উত্তর এল আবার সেই ফিসফিসে কণ্ঠে—“আমি যে গল্পটা শুরু করেছিলাম, কিন্তু শেষ করতে পারিনি।”
পর্ব ৪
লাইব্রেরির বাতাস ভারী হয়ে উঠল। গলার স্বরটা যেন দেয়াল ভেদ করে আসছে, চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে সায়ন্তনকে। তার মুঠোতে এখনও চেপে ধরা সর্বাণী কুণ্ডুর ডায়েরি। ঘরের বাতি টিমটিম করে জ্বলছে, জানলার ফাঁক গলে ঢুকছে চাঁদের আলো, যেন কোনো পুরোনো থিয়েটারের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে সে, যেখানে পরদা পড়েনি এখনো।
সে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলতে চাইল, কিন্তু দরজা আটকানো। বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেই যেন এক অদৃশ্য হাত ঠেলে ধরে রেখেছে। সে ধাক্কা দিল, কিন্তু কিছুতেই খুলল না। হঠাৎ দেওয়ালের পাশ থেকে বাতাস কেঁপে উঠল আর তার গালে ঠেকল ঠান্ডা নিশ্বাসের মতো কিছু—একটা কণ্ঠস্বর বলল, “তোর বাবাকে আমি মেরেছিলাম না। ও নিজেই নিজের অতীতকে দেখতে ভয় পেয়েছিল।”
সায়ন্তন তীব্র কাঁপা গলায় বলল, “তুমি সর্বাণী? তুমি বেঁচে আছো?”
কোনও উত্তর নেই। কেবল বাতাসের মধ্যে একফালি হাসির মতো কিছু ভেসে রইল। তারপর টেবিলের ওপর রাখা ডায়েরির পাতাগুলো আপনমনে ওল্টাতে শুরু করল—একটা, দুটো, তিনটে—হাওয়ার স্পর্শ ছাড়াই।
একটা পাতায় এসে থামল। সেখানে লেখা ছিল—
“বাবা-মা হারানোর পর যখন আমি এই বাড়িতে আশ্রয় নিই, তখন কেউ জানত না আমি আসলে কে। রায়চৌধুরি বাড়ির এক চাকরের মেয়ে, কিন্তু মেধার জোরে এই পরিবারে ঢুকতে পেরেছিলাম—গৃহশিক্ষিকার ছদ্মবেশে। সত্যিটা তখনই জানতাম, ওর বাবার কাছে একটা গোপন দলিল ছিল, যেটা আমি খুঁজছিলাম অনেক বছর ধরে।”
সায়ন্তনের মাথা চক্কর দিতে লাগল। অর্থাৎ সর্বাণী একজন গুপ্ত অনুসন্ধানকারী ছিলেন? তাঁর আগমন কেবল প্রেমের কারণে নয়, কোনো রহস্যের খোঁজে?
ঠিক তখন, ঘরের কোণে থাকা পুরোনো বুকশেলফের পেছন থেকে টুপ করে কিছু পড়ার শব্দ হল। সায়ন্তন এগিয়ে গিয়ে দেখল, একটা পাতলা খাম পড়ে আছে। সেটার গায়ে লেখা “আন্তরিকভাবে, বি.এ.”।
সে অবাক হল—বি.এ. কে? আবার নতুন কেউ? খামের ভিতরে একটা পুরনো চিঠি, তারিখ ১৯৮৪। তাতে লেখা—
“সর্বাণী, তুই ভুল জায়গায় খুঁজছিস। আসল নথিটা পুরোনো সুড়ঙ্গঘরের মেঝেতে পাথরের নিচে রাখা আছে। যদি সত্যিই জানতে চাস, তবে সায়ন্তনের বাবাকে বিশ্বাস করিস না—সে আমাদের ইতিহাস লুকিয়ে রাখছে।”
এই চিঠি সব বদলে দিল। তার বাবা, যার আত্মহত্যার রহস্য খুঁজতে সে এতদূর এসেছে, সেই কি সত্যিই কিছু লুকোচ্ছিলেন? কোনও এমন সত্য যা কাউকে জানাতে চাননি?
সায়ন্তন ডায়েরি, চিঠি, ছবি সব একত্র করে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। তার মাথার ভিতরে যেন এক ঝড় উঠেছে—প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা, লুকোনো ইতিহাস সব একসাথে মিশে যাচ্ছে।
ঠিক তখন, দরজাটা নিজে থেকেই খট করে খুলে গেল। করিডোরে হরিদাস দাঁড়িয়ে, মুখ ফ্যাকাশে, হাতে কেরোসিনের লণ্ঠন। সে ফিসফিস করে বলল, “বাবু, এক্ষুনি চলুন… ওই সুড়ঙ্গঘরটা… আমি জানি আপনি খুঁজছেন কোথায়।”
সায়ন্তনের চোখ জ্বলল, “তুমি জানো?”
হরিদাস মাথা নাড়ল, “আমি আর চুপ থাকতে পারি না। বারো বছর আমি ওই গোপনটা বুকের মধ্যে রেখেছি। চলুন বাবু, আজ রাতেই সব সত্যি আপনি জানবেন।”
সায়ন্তন তার সঙ্গে চলতে লাগল। করিডোর পেরিয়ে তারা উঠল পুরোনো সিঁড়িতে, যে সিঁড়ি অনেক বছর ধরে কেউ ব্যবহার করেনি। মাকড়সার জাল সরিয়ে, ধুলোয় পা চেপে তারা নামতে লাগল একটা অন্ধকার তলায়, যেখানে বাতাসও যেন কথা বলতে ভয় পায়।
নিচে পৌঁছে হরিদাস একটা পাথরের মেঝের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, “এই পাথরের নিচেই কিছু আছে বাবু… ওটাই সব শুরুর জায়গা।”
সায়ন্তন হাঁটু গেড়ে বসে পাথরটা ঠেলতে লাগল। পাথরটা নড়ল, তারপর ধীরে ধীরে উঠে এল—তার নিচে একটা ধাতব বাক্স। বাক্স খুলতেই একটা জীর্ণ কাগজ আর একটা মোটা রেজিস্টার বেরোল।
সায়ন্তন হাত কাঁপাতে কাঁপাতে কাগজটা খুলল, পড়ল—“রায়চৌধুরি এস্টেটের গোপন বিবরণ—জমিদার রঘুনাথ রায়চৌধুরির অবৈধ সম্পদ এবং সন্তান সম্পর্কে। সর্বাণী সেই সন্তানের উত্তরসূরি।”
পর্ব ৫
সায়ন্তনের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। রায়চৌধুরি এস্টেটের দলিল, তাতে লেখা—”সর্বাণী কুণ্ডু, রঘুনাথ রায়চৌধুরির অবৈধ কন্যা।” নিচে স্বাক্ষর রঘুনাথের নিজের হাতে। অর্থাৎ সর্বাণী শুধু এই বাড়ির অতিথি বা গৃহশিক্ষিকা ছিলেন না—তিনি ছিলেন এই রাজবাড়ির রক্তমাংসের উত্তরসূরি। অবৈধ, কিন্তু বৈধ দাবিদার।
তার মাথায় যেন এক ঝাঁক শব্দ একসাথে বাজতে লাগল—তার বাবার আতঙ্কিত মুখ, রাতের পিয়ানো, সেই চোখে চোখ পড়া সাদা-কালো ছবির নারী, হঠাৎ এক মুহূর্তে সব স্পষ্ট হতে শুরু করল। তার বাবা জানতেন। জানতেন সর্বাণী কে। আর সেই সত্যি চিরকাল চাপা দিতে চেয়েছিলেন।
সায়ন্তন সেই রেজিস্টারটা খুলে দেখল, তাতে একের পর এক খরচের হিসেব, চেক নম্বর, এবং সবশেষে একটি নাম ঘুরে ফিরে এসেছে—”বি.এ.” সেই লোক সর্বাণীকে সাহায্য করছিল গোপনে। কে ছিল এই বি.এ.? বাড়ির কেউ, না বাইরের কেউ?
হরিদাস পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় বলল, “বাবু, আমি জানতাম, কিন্তু কিছু বলিনি। সাহস হয়নি। আপনার বাবা খুব বদলে গিয়েছিলেন সর্বাণী মেমসাহেব চলে যাওয়ার পর।”
সায়ন্তন ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, “কেন চলে গিয়েছিলেন? তাঁকে কি তাড়ানো হয়েছিল?”
হরিদাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, “একরকম তেমনই। উনি যখন তার দাবিদার পরিচয় আনতে চাইলেন, বাড়ির লোকেরা চুপিচুপি ওনার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে লাগল। আপনার বাবা, মানে শ্রীযুক্ত অরিজিৎবাবু, প্রথমে বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু পরে… পরে হয়তো বুঝেছিলেন তিনি ভুল করেছেন। কিন্তু ততদিনে সর্বাণী মেমসাহেব এই বাড়ি ছেড়ে কোথায় উধাও।”
সায়ন্তনের মুখ শুকিয়ে গেল। যদি সর্বাণী সত্যিই চলে যান, তাহলে রাতের পিয়ানোর সুর কে বাজায়? সেই ক্লিপ, সেই গলা?
সে নিচু স্বরে বলল, “সর্বাণী কি মারা গিয়েছিলেন এখানে?”
হরিদাস নড়ে উঠল, “সে আমি জানি না বাবু। কিন্তু একটা রাত মনে আছে। আপনার বাবা বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘সর্বাণী! আমি ভুল করেছি! ক্ষমা করো!’ এরপর দুদিন কিছু খাওয়াদাওয়া করেননি। তারপর… সেই লাইব্রেরি…”
সব জুড়ে এক অলিখিত সুতোর মতো গল্প এগিয়ে চলেছে, যার ডগায় দাঁড়িয়ে আছে সায়ন্তন। ঠিক তখনই রেজিস্টারের একদম শেষ পাতায় একটা ছোট চিরকুট পড়ে থাকল। তাতে লেখা—
“বি.এ.র সঙ্গে সর্বশেষ দেখা হল ১৯৮7 সালের জুলাই। রাত্রি ৩টার সময় সে এসেছিল পিছনের বাগানে। ও বলেছিল, ‘আমি যাবো, কিন্তু সত্যিটা একদিন কেউ জানবেই।’ সেই চাবি, সেই ঘর—সব ওর জন্য রেখে গেলাম।”
সায়ন্তন পকেট থেকে সেই লোহার চাবিটা বের করল—যেটা সর্বাণীর কুলুঙ্গি থেকে পেয়েছিল। তাহলে কি এই চাবিটাই সেই ঘরের, যেখান থেকে সত্যি প্রকাশ পাবে?
হরিদাস চাবিটার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, “এইটা তাহলে… ওই বাগানের দোতলা ছাউনির নিচের সিন্দুকঘরের চাবি বাবু। যেটা অনেক বছর আগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।”
সায়ন্তনের মুখে স্থির সংকল্প ফুটে উঠল। “আমাকে এখনই সেখানে নিয়ে চলো।”
তারা আবার ফিরে চলল বাড়ির পেছনের দিকে। বাঁশবনের গায়ে একটা পুরোনো ইটের ঘর, যার নিচে ছিল একটা লোহার দরজা। চাবি ঢোকাতেই একটা খটখটে আওয়াজে খুলে গেল তালা। সিঁড়ি ধরে নিচে নামতেই একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, আর বাতাসে ঘর্মাক্ত লবণের গন্ধ।
ঘরের মধ্যে একটা বড় কাঠের টেবিল, তার ওপর রাখা একগুচ্ছ পুরোনো কাগজ। সেইসব কাগজ ঘেঁটে সায়ন্তন দেখল একটার পর একটা জমির দলিল, যার সব ক’টিই সর্বাণীর মায়ের নামে লেখা।
আর ঘরের এক কোণে ধুলো পড়া একটা কাঠের বাক্স—ভেতরে একগুচ্ছ চিঠি, যার উপরে লেখা নাম—”বিমল আচার্য, ওকালতি সহকারি।”
সায়ন্তনের ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল। বি.এ. মানে বিমল আচার্য?
সে একটা চিঠি খুলে পড়তে লাগল—“সর্বাণী, আমি জানি এই লড়াই একা তোমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমি তোমার পাশে আছি। যদি কিছু হয়, এই কাগজগুলো সায়ন্তন রায়চৌধুরির হাতে একদিন পৌঁছবে, এই বিশ্বাসেই আমি এগোচ্ছি…”
বুকের ভেতর কিছু একটা চুঁইয়ে পড়ল—একটা ইতিহাস, যা দাগ রেখে গেছে আত্মার গায়ে। আর তখনই আবার ঘরের বাতাসে সেই কণ্ঠস্বর—
“তুই সত্যিটা খুঁজে পেয়েছিস সায়ন্তন। এখন শুধু শেষ মুখটা দেখা বাকি।”
পর্ব ৬
বাতাস হঠাৎ ঘন হয়ে উঠল। ঘরের বাতি টিমটিম করছে, আর কাঠের মেঝেতে যেন কারও অদৃশ্য পায়ের শব্দ বাজছে—একটা, দুইটা, থেমে থেমে। সায়ন্তন স্থির দাঁড়িয়ে রইল, হাতে বিমল আচার্যের সেই চিঠি। শব্দটা ঘরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে সরছে, যেন কেউ অন্ধকারে হাঁটছে, তাকে ঘিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না।
সে সাহস করে বলল, “তুমি সর্বাণী? আমি এখন জানি তুমি কে ছিলে, কেন এসেছিলে, কী লুকোনো ছিল… তুমি কি এখনও এখানে আছো?”
কোনও জবাব নেই। কিন্তু তার কানে ভেসে এল একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ, তারপর ঘরের মাঝখানে রাখা টেবিলের ওপর বাতাসে হালকা আন্দোলন। কাগজগুলো একসাথে নড়ে উঠল, আর একটা পৃষ্ঠা উড়ে এসে পড়ল তার পায়ের কাছে।
সে কাগজটা তুলল। এটা ছিল এক মেডিকেল রিপোর্ট। তারিখ ১৯৮৬। রোগীর নাম: সর্বাণী কুণ্ডু। রিপোর্টে লেখা ছিল: “মৃদু মানসিক অসুস্থতা, অবসাদ, বাস্তবতা ও বিভ্রমের সীমারেখা অস্পষ্ট। অবিলম্বে পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।”
সায়ন্তন থমকে গেল। তাহলে সর্বাণী কি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন? নাকি এটা কেবল একটি দাগ দেওয়ার কৌশল ছিল? কোনও একজন মহিলাকে, যিনি সত্য দাবিদার, তাকে ‘পাগল’ প্রতিপন্ন করলে তো সমাজ সহজে বিশ্বাস করে। এই কৌশল তো বহুবার ইতিহাসে ব্যবহৃত হয়েছে।
সে চেয়ারের পাশে রাখা সেই বাক্সে চোখ রাখল। ভেতরে ছিল সর্বাণীর ব্যক্তিগত জিনিস—একটা ছোট আয়না, সাদা চুড়ি, একটি চিঠি, যার খামের ওপরে শুধু লেখা—“চোখের গভীরে এক বাড়ি আছে, যেখানে আমি থাকি। যেদিন কেউ সেই চোখে তাকাবে, আমি আবার ফিরে আসব।”
সায়ন্তনের হাত কেঁপে উঠল। এই বাক্যটা সে অনেক আগে শুনেছে। তার মা একদিন বলেছিলেন, “তোর বাবার একটা রোগ ছিল—সে মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে বলত, ‘চোখের মধ্যে একটা বাড়ি আছে, আমি ওখানে আটকে গেছি।’”
তবে কি এই বাক্য সর্বাণীর, যা তার বাবা হৃদয়ে বয়ে নিয়ে ঘুমের ঘোরেও উচ্চারণ করতেন?
ঠিক তখনই ঘরের দরজায় টোকা পড়ল—তিনবার, ধীরে ধীরে।
সে দম আটকিয়ে দরজার দিকে তাকাল। বাইরে কেউ নেই। কিন্তু মেঝেতে দেখা গেল একজোড়া ছাপ—পায়ের ছাপ, যেগুলো কাদামাটি মাখা, ঘরের ভিতরে আসছে… অথচ কেউ চোখে পড়ছে না।
সে ধীরে ধীরে দরজা ঠেলে বাইরে এল। পেছনের বাগানে তখন পূর্ণিমার আলো, মাটির ওপর সেই ছাপগুলো সোজা এগিয়ে চলেছে বাড়ির একদম পুরোনো পেছনের অংশের দিকে, যেটা বহু বছর ধরে বন্ধ ছিল—মধ্যভাগে একটা বদ্ধ ঘর, যার জানালা জং ধরা লোহার।
সে ছুটে চলল সেই দিকেই। পায়ের ছাপ যেখানে থেমেছে, সেখানে একটা প্রাচীন দরজা। সে চাবি ঢুকিয়ে দরজাটা খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু সেটা খুলল না। ঠিক তখনই বাতাসে সেই কণ্ঠস্বর ফিরে এল—“এই দরজা চাবি দিয়ে খুলবে না, এই দরজা খুলবে চোখ দিয়ে।”
সে মুহূর্তে বুঝল—এই দরজার মানে হয়তো বাস্তব দরজা নয়। হয়তো এই দরজা তার নিজের ভেতরে, তার নিজস্ব চোখের মধ্যে কোনও অতীতকে চেনার, মেনে নেওয়ার, আত্মস্থ করার এক অভ্যন্তরীণ প্রবেশপথ।
সে চোখ বন্ধ করল। মনের চোখে সর্বাণীর মুখ আঁকতে চাইল। সেই ক্লিপ, সেই পিয়ানোর সুর, সেই লাল কালি… হঠাৎ মনে হল, লাইব্রেরির পুরোনো ছবিগুলোর ভেতরে একটা মুখ সে আগে লক্ষ করেনি—একটা গ্রুপ ছবির পেছনে দাঁড়ানো একজন নারী, যার চোখ সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ছিল, যেমনটা ডায়েরিতে বলা হয়েছিল।
সে দৌড়ে লাইব্রেরিতে ফিরে এল। সেই ছবি আবার খুঁজে বের করল। এবার ভালো করে দেখল—হ্যাঁ, ওই নারীর চোখের মধ্যে কিছু ছিল। সে তার ফোনে ছবি তুলে জুম করে দেখতে লাগল। আর তাতে দেখা গেল চোখের ভেতরে এক প্রতিবিম্ব—একটা ঘরের দরজা, যেটার গায়ে আঁকা সেই চক্রচিহ্ন, আর ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষ—কে সে?
হঠাৎ ফোন নিভে গেল। আলো চলে গেল ঘরের। আর আবার সেই কণ্ঠস্বর—
“তুই সত্যি যদি খুঁজতে চাস, তাহলে তাকাস না কেবল সামনে। পেছন ফিরে দেখ—কার মুখ তুই ভুলে গেছিস।”
পর্ব ৭
ঘরের অন্ধকার যেন চাপা দুঃস্বপ্নের মতো সায়ন্তনের ঘাড়ে এসে বসে। সেই কণ্ঠস্বর—ফিসফিসে, অথচ শিরার ভিতর কাঁপন ধরানো—বলছে, “পেছন ফিরে দেখ।”
সে ধীরে ধীরে ঘুরল। আলো নেই, কেবল জানালার ফাঁক গলে আসা চাঁদের আভা। ঘর নিঃশব্দ, কিন্তু দেওয়ালের ছায়া যেন বদলে গেছে। একটা ছায়া, যেটা তার নিজের না, দাঁড়িয়ে ছিল জানালার ঠিক সামনে। সে আবার ঘুরে তাকাল—কেউ নেই। তবু বুক ধড়ফড় করছে।
সে নিজের কাছে ফিসফিস করে বলল, “মুখ যার দেখিনি কোনওদিন—তাহলে সে কি সর্বাণী নয়? তাহলে কে?”
হঠাৎ মনে পড়ল পুরোনো ফটোগ্রাফের সেই চোখের প্রতিবিম্ব। সে আবার ফোন খুলে ছবিটা বের করল। জুম করে তাকাতেই এবার স্পষ্ট বোঝা গেল—চোখের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ব্যক্তিটি একজন পুরুষ। মাথায় টুপি, মুখে হালকা দাড়ি। কিন্তু তার চেহারাটা অদ্ভুতভাবে মিল খাচ্ছে কারও সঙ্গে… তার বাবার সঙ্গে!
সে অবাক হয়ে বলল, “এটা তো বাবার মতই দেখতে… কিন্তু বাবা তো ক্যামেরার সামনে ছিলেন। তবে এটা কে?”
তখনই মনে পড়ল সর্বাণীর ডায়েরির সেই শেষ অংশ—যেখানে লেখা ছিল, “প্রতিটি ছায়ারও একটা ছায়া থাকে। আমি যাকে ভালোবেসেছিলাম, সে হয়তো একজনের ছায়া ছিল মাত্র।”
সে ছুটে লাইব্রেরির আলমারি খুলল। সেখানে পুরোনো ফাইল, কিছু সনদ, পুরাতন পোস্টকার্ড। একটা চিঠি পাওয়া গেল, প্রেরক—বিমল আচার্য। ঠিকানায় লেখা R.C. Cottage, Jharkhali Branch Estate।
সে চিঠি খুলে পড়ল—
“অরিজিৎবাবু, আমি জানি আপনি আমায় চেনেন না, কিন্তু আমি সর্বাণীর হয়ে অনুরোধ করছি—তাকে আর চাপ দেবেন না। ও আপনাকে কিছু বলেনি, কিন্তু আপনি তো জানেন না—আপনার যমজ ভাই আজও বেঁচে আছে।”
সায়ন্তনের হাত থেকে কাগজ পড়ে গেল। যমজ ভাই?
সে কোনদিন শুনেনি তার বাবার যমজ ভাই ছিল। এই তথ্য পুরো গল্পটাই উলটে দিল। তাহলে কি ছবিতে দাঁড়ানো লোকটি তার বাবার যমজ ভাই? আর সেই ছায়ার জীবনই কি সর্বাণীর ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু ছিল?
সে গুছিয়ে বসে পড়ল। তার সামনে এখন একটি পূর্ণ গোলক, যার প্রতিটি বিন্দুতে রয়েছে ধোঁয়াশা, কিন্তু একটিই কেন্দ্রে সত্য—একজন পুরুষ, যাঁর পরিচয় চাপা পড়ে গেছে ইতিহাসে।
সে হরিদাসকে ডেকে পাঠাল। বৃদ্ধ এসে দাঁড়াল চুপচাপ।
“হরিদাস, আমার বাবার যমজ ভাই ছিল?”
হরিদাস চুপ। চোখ নামিয়ে বলল, “আপনার ঠাকুরদা রঘুনাথবাবুর দুই ছেলে ছিল। কিন্তু ছোট ছেলেটিকে নাকি জন্মের পর থেকেই দূরে পাঠানো হয়েছিল। কেউ বলত দুর্বল শরীর, কেউ বলত অন্য কিছু। কেউ ওর নামটাও জানত না। ওর পরিচয় মুছে ফেলা হয়েছিল। শুধু বাড়ির পুরোনো নথিতে একবার দেখেছিলাম নাম—অরিন্দম রায়চৌধুরি।”
সায়ন্তনের চোখ ফাঁকা হয়ে গেল। অরিজিৎ ও অরিন্দম—যমজ, দুই বিপরীত জীবন, একটিকে আলোতে রেখে অন্যটিকে অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হয়েছে।
হরিদাস চাপা গলায় বলল, “সর্বাণী মেমসাহেব সম্ভবত অরিন্দমবাবুকে ভালোবেসেছিলেন। আর আপনার বাবা, হয়তো এই সম্পর্ক জানতেন না শুরুতে… পরে জেনেছিলেন, বুঝেছিলেন… তাই হয়তো তিনি নিজেও পুড়তে শুরু করেছিলেন ভিতর থেকে।”
এইবার সমস্ত টুকরো যেন একজায়গায় এসে পড়ল।
সায়ন্তনের মাথায় এখন স্পষ্ট একটা দৃশ্য ভেসে উঠছে—সর্বাণী, এক অন্ধকার বংশপরিচয় নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছেন। অরিন্দম, এক বিস্মৃত ভাই, যিনি হয়তো কখনোই চাননি নিজের পরিচয় ফিরে পেতে। অরিজিৎ, দুই পক্ষের টানাপোড়েনে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন।
ঠিক তখনই বাড়ির পেছন থেকে আবার সেই পিয়ানোর সুর ভেসে এল—একই ছন্দ, একই ভুলে থেমে যাওয়া সুর, বারবার বাজছে। সে ছুটে চলল সেই দিকে। লাইব্রেরির পেছনের ঘরে, যেখানে পুরোনো পিয়ানো রাখা আছে।
ভিতরে ঢুকতেই সে দেখল—পিয়ানো বন্ধ, কিন্তু চেয়ার দুলছে। কেউ সবে উঠেছে যেন।
আর সেখানে, আলো-আঁধারির মাঝে, দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন ছায়ামূর্তি। মুখ দেখা যায় না, কিন্তু হাত বাড়িয়ে সায়ন্তনের দিকে ইশারা করছে।
সায়ন্তন ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। এবার মুখ দেখবে সে—মুখ, যার মুখ সে কখনো দেখেনি… কিন্তু যার ছায়া তার পরিবারকে চিরকাল তাড়া করেছে।
পর্ব ৮
সায়ন্তনের পা যেন ভার হয়ে গেছে। প্রতিটি ধাপে সে কাছে এগোচ্ছে ছায়ামূর্তির, কিন্তু মনে হচ্ছে এই পথ সে একবার আগেও হেঁটেছিল—হয়তো কোনো স্বপ্নে, কোনো অবচেতনে। ছায়াটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। মাথায় হালকা টুপি, মুখে পাতলা দাড়ি, পরনে সাদা পাঞ্জাবি। সেই মুখ… যেন তার বাবারই মুখ, কিন্তু তাতে বিষাদের এমন ছায়া যে, তা অরিজিৎ রায়চৌধুরির নয়—এ শুধুই অরিন্দম রায়চৌধুরির।
ছায়ামূর্তিটা চেয়ারে বসে পড়ল। আর হাত দিয়ে দেখাতে লাগল পিয়ানোর কিবোর্ডের দিকে। সে বলল না কিছু, কিন্তু সায়ন্তন বুঝতে পারল—ও চায়, সে বাজাক সেই সুর। সে ধীরে ধীরে হাত রাখল কিবোর্ডে, মনে করে সেই ছন্দ, যা বহুবার শুনেছে রাতের নিস্তব্ধতায়।
একটা ভুল-ভুল সুর। বারবার থেমে যাওয়া। সায়ন্তন এবার সেই সুর সম্পূর্ণ করে বাজাল—একটা সুর, যা শেষ অবধি পৌঁছল। মুহূর্তে ঘরের বাতাসে যেন কাঁপন উঠল। ছায়ামূর্তিটা মাথা ঝুঁকিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল, ঠিক যেন একটা ধোঁয়ার দাগ—চোখের সামনে থেকেও অদৃশ্য।
ঠিক তখনই ঘরের এক কোণে রাখা ছোট কাঠের বাক্স খুলে পড়ল মাটিতে। সায়ন্তন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখল ভেতরে রাখা একটা চিঠি, যার ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা—“আমার শেষ সন্ধে—অরিন্দম।”
সে চিঠি খুলে পড়তে লাগল—
“আজ ১৯৮৭ সালের শেষ সন্ধে। আমি জানি, আমি আর এই বাড়িতে থাকতে পারব না। আমি তো কখনোই ছিলাম না। জন্মের পর থেকেই আমাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, আমার কোনও পরিচয় ছিল না, কেবল ছায়ার মতো ছিলাম। যখন সর্বাণী এলো, মনে হল আমি কেউ হতে পারি। ও আমাকে মানুষ ভাবত। কিন্তু ওর পরিচয় জানার পর, বুঝলাম আমরা দুই হারিয়ে যাওয়া ছায়া—কেউ আলোর নিচে আসার সুযোগ পাইনি।”
“ভাই অরিজিৎ জানত না, আমি তারই ছায়া। আমি আমার সত্তা চাইনি, কেবল স্বীকৃতি চেয়েছিলাম। কিন্তু ও যখন বুঝল সর্বাণী আমায় ভালোবাসে, ওর চোখে যে দৃষ্টি দেখেছিলাম, তাতে আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমি জানি, ও আমায় শেষমেশ বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু সময় ফুরিয়ে গিয়েছিল।”
“এই চিঠি আমি রেখে যাচ্ছি যদি কোনোদিন কোনও উত্তরসূরি এসে প্রশ্ন করে—কে ছিল এই ছায়ামানব? সায়ন্তন, যদি তুই পড়িস, জানিস—তোর বাবার মতো তুই যেন নিজের ভেতরের ছায়াকে দমন করিস না। প্রশ্ন করিস, সন্দেহ করিস, আর যা সত্যি মনে হয়—তা খুঁজে বের করিস।”
সায়ন্তনের চোখে জল চলে এলো। এই মুহূর্তে যেন সমস্ত অতীত, সমস্ত দুঃস্বপ্ন, সমস্ত রহস্য একসাথে ভেঙে পড়ছে তার মাথার ওপর। কিন্তু তার ভেতরেও যেন জন্ম নিচ্ছে এক রকম শান্তি—একটা বন্ধ দরজা যেন এখন আস্তে আস্তে খুলছে।
পিয়ানোর সামনে সে বসে রইল কিছুক্ষণ। তার মনে হল, সর্বাণীও কোথাও আছেন, হয়তো আর কোনও ছায়ায়, হয়তো আলোয়। আর অরিন্দম? তিনি কি মুক্তি পেলেন? সেই উত্তর হয়তো কোনোদিনই জানা যাবে না।
কিন্তু ঠিক তখনই ঘরের জানালায় কার যেন হাত ছোঁয়ার শব্দ। সে উঠে বাইরে তাকাল—জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ির বাগানে দাঁড়িয়ে এক নারী। মুখ দেখা যায় না, কিন্তু সেই ক্লিপ, সেই সাদা শাড়ি—সর্বাণী।
তাকে দেখে সায়ন্তনের ঠোঁটে একফালি হাসি এল। সে জানে, ও কিছু বলবে না। শুধু দেখবে। আর সে জানে, আজ রাতটা সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।
পর্ব ৯
বাগানের ছায়ায় দাঁড়ানো সেই নারীর মুখটা ঠিক বোঝা যায় না, তবু সায়ন্তন জানে—ওই সর্বাণী। ওর উপস্থিতি ঘিরে এক ধরণের শান্তি, যেন ঘূর্ণির কেন্দ্রে এক বিন্দু নিস্তব্ধতা। সে কিছু বলে না, এগিয়েও আসে না, কেবল দাঁড়িয়ে থাকে। ঠিক যেমন থাকে সেইসব চরিত্ররা, যাদের রাতের গল্পে মনে রাখা হয়, কিন্তু সকালে নাম মনে পড়ে না।
সায়ন্তনের মন জুড়ে তখন একটাই প্রশ্ন—সর্বাণী কি এখনো আটকে আছেন? ও কি মুক্তি পেয়েছে? না কি, এই বাড়ির প্রতিটি দেয়ালে, প্রতিটি ঘরে তার চিহ্ন রয়ে গেছে—এক অনুচ্চারিত ইতিহাসের মতো?
সে ধীরে ধীরে নিচে নেমে বাগানের দিকে এগোল। হাঁটার পথে শিউরে উঠল গায়ে—মাটি স্যাঁতসেঁতে, বাতাসে গোলাপ আর পুড়নো কাঠের গন্ধ। যখন বাগানের একদম প্রান্তে পৌঁছল, তখন কেউ নেই। সর্বাণী চলে গেছেন। তবে তার থাকার ছাপ রয়ে গেছে। মাটির ওপরে দেখা যাচ্ছে পদচিহ্ন, ফুলের ওপর একটুকরো ভেজা ওড়নার ঘষা।
সে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাবল, এতদিন ধরে যা তাকে তাড়া করেছে—ভয়ের মতো, কৌতূহলের মতো—সবই আজ এত কোমল লাগছে। যেমনটা হয়, যখন কোনও পুরনো শত্রুর মুখোমুখি হয়ে দেখা যায়, সে আসলে কখনো শত্রু ছিল না—শুধু একটা ভুল বোঝাবুঝি।
ঠিক তখনই পেছন থেকে একটি গলা ভেসে এল, “সব খুঁজে পেলে বাবু?”
হরিদাস দাঁড়িয়ে, লণ্ঠন হাতে। আলোয় তার মুখে যেন গভীর দুঃখ আর শান্তির মিশ্রতা।
সায়ন্তন বলল, “হ্যাঁ… অথবা যতটা পারা যায় ততটাই। তুমি কি জানো, অরিন্দমবাবু কোথায় গেলেন?”
হরিদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “না বাবু। কেউ জানে না। একরাতে উনি গিয়েছিলেন, আর ফেরেননি। কারওর মতে ওঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল দূরে। কারও মতে… হয়তো তিনি নিজেই হারিয়ে গিয়েছিলেন নিজের ছায়ার ভিতরে।”
সায়ন্তন মাথা নিচু করে বলল, “আমার বাবা… আমার ধারণা ও বুঝেছিলেন সবটাই শেষে। কিন্তু ততদিনে সর্বাণীও চলে গিয়েছিলেন।”
“হয়তো তাই বাবু। তাই তিনি চুপচাপ লাইব্রেরির সেই ঘরে বসে থাকতেন। আমি দেখেছি—ঘন্টার পর ঘন্টা একা বসে থাকতেন পিয়ানোর সামনে, বাজাতেন না, শুধু তাকিয়ে থাকতেন।”
সায়ন্তন জানে, তার বাবার সেই নীরবতা ছিল অনুশোচনার। সেই সব কথা না বলা ভালোবাসা, যা ছিঁড়ে যায় শুধু সমাজের ‘বৈধতা’র শিকলে।
সে আবার ফিরে এলো লাইব্রেরিতে। জানালা দিয়ে আলো ঢুকছে ধীরে ধীরে। প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। পাখিরা ডাকছে দূরে কোথাও।
টেবিলের ওপর রাখা আছে সর্বাণীর ডায়েরি, অরিন্দমের চিঠি, দলিলপত্র—সব কিছুই যেন একটি শেষ নৈবেদ্য, যা এখন সে গুছিয়ে রাখবে।
সে ডায়েরির শেষ পাতায় একটা লাইন লিখল—
“আমি দেখেছি সেই মুখ, যাকে কেউ মনে রাখে না। আমি শুনেছি সেই সুর, যেটা ভুলে যাওয়া যায় না।”
ঠিক তখন, বাইরে একটা গাড়ির হর্ণ। শহর জেগে উঠছে। দিনের আলোয় এই বাড়ির দেয়াল আর কুয়াশা একসাথে মিলিয়ে যেতে শুরু করছে।
কিন্তু সায়ন্তন জানে—এই বাড়ি, এই পিয়ানো, এই ডায়েরি, এই সব ছায়া—সবই থাকবে। শুধু বদলে যাবে এক একটি নাম। আর কেউ একজন, কোনও ভবিষ্যতের উত্তরসূরি, হয়তো আবার একদিন ফিরে আসবে এই ‘অলীক ধোঁয়া’র মধ্যে।
পর্ব ১০
ভোরের আলোয় রায়চৌধুরি বাড়ির রং বদলে যায়। রাতের ছায়া আর রহস্যের জাল যেন ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। পাখির ডাক, দূরের ট্রাম লাইনের ঝনঝন, সব মিলিয়ে যেন বাস্তব ফিরে এসেছে। কিন্তু সায়ন্তনের মনে হয়, এই বাড়ির দেয়ালের ভিতরেও এখনও কেউ হাঁটছে—আলো আর অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা অতীতেরা।
সে একে একে সব জিনিস গুছিয়ে রাখে—সর্বাণীর ডায়েরি, অরিন্দমের চিঠিগুলো, জমির পুরোনো দলিল। প্রতিটি কাগজ এক একটি গল্প, এক একটি জীবনের অজানা বাঁক। একটিও সে ফেলে দিতে পারে না। সবই সত্যি, অথবা… সবই ধোঁয়া।
সে জানে, তাকে এই শহরে ফিরতে হবে, আবার অফিস, আবার মেট্রো, আবার কর্পোরেট জগত। কিন্তু এবার সে যে সত্যটা সঙ্গে নিয়ে ফিরছে, তা শুধু পারিবারিক ইতিহাস নয়, একটা আত্মপরিচয়—সে আর কেবল অরিজিৎ রায়চৌধুরির ছেলে নয়, সে সেইসব মানুষের উত্তরসূরি যারা তাদের পরিচয় হারিয়ে ফেলেও একটুকরো সত্য ধরে রেখেছিলেন।
হরিদাস এগিয়ে এসে বলল, “বাবু, সব পেয়ে গেলেন?”
সায়ন্তন শান্ত গলায় বলল, “সব না। কিন্তু যা দরকার, তার সবটাই। বাকিটুকু থাকুক এখানে।”
সে চলে যাওয়ার আগে লাইব্রেরির মাঝখানে রাখা পিয়ানোর ওপর রেখে গেল সর্বাণীর ডায়েরি আর অরিন্দমের শেষ চিঠি। পাশে একটা ছোট্ট চিরকুট—
“যদি কেউ একদিন ফিরে আসে, যেন সে জানে—এই গল্পটা কোনওদিন হারায়নি। শুধু অপেক্ষা করেছিল চোখের গভীরে একজন পাঠকের জন্য।”
গাড়িতে উঠে সে শেষবারের মতো পেছনে তাকাল। বাড়িটার জানালায় হালকা বাতাসে পর্দা দুলছে। ঠিক যেন কেউ দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে, বিদায় জানাচ্ছে নিঃশব্দে।
গাড়ি চলতে শুরু করল। শহর ঘুম ভেঙে উঠছে। রাস্তার মোড়ে লাল সিগন্যালে দাঁড়িয়ে সায়ন্তন নিজের প্রতিবিম্ব দেখল কাচে—চোখে এখন আর কেবল সন্দেহ নেই, আছে একটা নিঃশব্দ বোঝাপড়া।
তার মনে হল, ছায়াগুলো হয়তো সত্যের চেয়ে বেশি স্পষ্ট।
সত্য কখনো একরঙা নয়।
আর সেই কারণেই, আমরা অনেক সময় ছায়া ধরে সত্যকে চিনে নিই।
শেষ